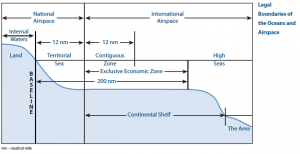যতদূর মনে পড়ে, এবনে গোলাম সামাদের প্রথম যে বই আমার হাতে আসে, তার নাম বাংলাদেশে ইসলাম (প্রকাশ-১৯৮৭) বইটি এসেছিল কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যই। বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য এ বইয়ে বিভাসিত, তা আমাকে এবনে গোলাম সামাদে আগ্রহী করল তুমুল। একে একে পড়া হলো তার ‘নৃতত্ত্ব’, ‘উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব¡’, ‘প্রাথমিক জীবাণুতত্ত্ব’, ‘উদ্ভিদ সমীক্ষা’, ‘শিল্পকলার ইতিকথা’, ‘ইসলামী শিল্পকলা’, ‘মানুষ ও তার শিল্পকলা’। বহুবিস্তারি এই মানুষ নতুন অর্থে হাজির হলেন আমার চৈতন্যে। মনে হলো তিনি সম্পন্নতার মধ্যে জীবনের অর্থ লাভ করেছেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রাণ একাকার হয়ে তাকে সম্পন্ন করছে। শিল্পকলার সাথে তার আত্মার যোগ না থাকলে তার শিল্প সমালোচনা এত প্রাণবাহী হতো কিভাবে? পরে নিশ্চিত হলাম, কৈশোর থেকে তার মনে বাস করত শিল্পকলার শিশু। বড় হয়ে শিল্পী হবেন, এমন অভিপ্রায়। স্বপ্নকে তিনি ক্যানভাসে না আঁকলেও হয়ে ওঠেন শিল্পতাত্ত্বিক। জীবনভর বসবাস করেছেন শিল্পে। গ্রন্থাবলি ছিল সেই যাপনের চিত্রায়ণ।
কিন্তু তার যাপন শিল্পকলার মাটি কামড়ে বসে থাকেনি। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ছিল সহজাত বিচরণভূমি। প্রতিটি গ্রন্থে, এমনকি ক্ষীণদেহী প্রবন্ধে তিনি উগরে দিতেন এর প্রাণরস। সত্যের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ছিলো নির্মোহ। যুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বে শুধু যুক্তিতে তার সায় ছিল না, গভীরভাবে অভিজ্ঞতাবাদী ছিল তার মন। তিনি জানতেন, যুক্তির সীমাবদ্ধতা। যেখানে অভিজ্ঞতা অনিবার্য, সেখানে যাচাই ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ছিল তার বিচারশীলতার সাথে সঙ্গতিশীল। ফলত তিনি সমাজ, নন্দনতত্ত্ব এমনকি ইতিহাস বিচারে বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী থাকতে পেরেছেন। আরো পরে তার ‘বাংলাদেশের মানুষ ও ঐতিহ্য’, ‘বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি’, ‘বর্তমান বিশ্ব ও মার্কসবাদ’, ‘আত্মপক্ষ’, ‘আত্মপরিচয়ের সন্ধানে’ ‘বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া’, ‘আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা এবং আরাকান সঙ্কট’, ‘বায়ান্ন থেকে একাত্তর’, ‘রাজনীতিবিষয়ক নির্বাচিত কলাম’, ‘আমার স্বদেশ ভাবনা’ গ্রন্থে তিনি নিজেকে আরো প্রসারিত করেন। সেই প্রসারণে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞান ও চিন্তার বিউপনিবেশায়নে তার কণ্ঠস্বর একটি এমন সম্ভাবনা হয়ে হাজির হয়, যার রয়েছে নিবিড় উপযোগ।
জুসেফ আশিল এমবেম্বে (Joseph-Achille Mbembe; জন্ম : ১৯৫৭-) বলেছিলেন, জ্ঞানের বিউপনিবেশায়নের অর্থ হলো পশ্চিমা কর্তৃত্ববাদী জ্ঞানবিজ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যা পশ্চিমা জ্ঞানব্যবস্থার বাইরে থেকে আগত কল্পনা এবং তার বাইরে সূচিত ও সূত্রবদ্ধকৃত যেকোনো চিন্তাধারাকে কঠোরভাবে দমন করে। এবনে সামাদের কলম কাজ করেছে সেই জায়গায়, যাকে পশ্চিমা জ্ঞানশাসন কঠোর হাতে দমন করে। তিনি আমাদের স্বকীয় পরিচয় সূত্রবদ্ধ করেছেন। চাপিয়ে দেয়া বয়ানের উপর নির্ভরতা পরিহার করেছেন, বিশেষত যে বয়ান ঔপনিবেশিক প্রকল্পের বাবু বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্র করেছেন।
এবনে সামাদ রাষ্ট্রকৃত সেই প্রোপাগান্ডাকে কেবল এড়িয়ে যাননি, নিজের ও সমষ্টির অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও দর্শনের আওতায় করেছেন আমাদের নিজস্ব তত্ত্বায়নও। উপমহাদেশীয় ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিক মন আমাদেরকে যেভাবে দেখে ও দেখায়, তার বিপরীতে এ ছিল এক প্রতিরোধ, মুক্তিপ্রচেষ্টা। ‘চাপিয়ে দেয়া জ্ঞান, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভরতা বন্ধ করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বিশ্ব-দর্শনের ভিত্তিতে কোনো কিছুর তত্ত্বায়নকে যখন আমরা বিউপনিবেশায়ন বলে ভাবি, তখন এবনে সামাদ বিশেষ তাৎপর্য বহন করেন।
একেবারে আত্মপরিচয়ের গোড়া থেকে তার যে লড়াই, সেটি বোঝার চেষ্টা একটি বড় রচনা দাবি করে। কিন্তু আমাদের কথা বলতে হচ্ছে দ্রুতলয়ে। নৃতত্ত্বে তার পর্যবেক্ষণের বিষয়টি ধরা যাক। এখানে চেহারার বিচারে মানুষকে চারটি ভাগে ফেলা হয়। সেগুলো হচ্ছে, ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রোয়েড ও অস্ট্রালয়েড। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষকে তিনি দেখেছেন ‘ককেশয়েড বিভাগে।’ আমরা জানি, ককেশয়েডদের দেহের আকৃতি বলিষ্ঠ, শক্তিশালী ও লম্বা। ককেশয়েডদের গায়ে লোম ও মুখে প্রচুর দাড়ি আছে। গায়ের রং সাদা ও সাদা-লালচে। চুলের রং বাদামি ও সোনালি এবং চুল চিকন ও মোটা সোজা ধরনের। কান মাঝারি ধরনের লম্বা ও প্রশস্ত। ঠোঁট পাতলা, চোখের রং হালকা থেকে বাদামি কালো এবং চোখের মণি নীল, নাক চিকন ও উঁচু, মুখ লম্বাটে ও সরু, আর মাথা হয় লম্বাটে। সামাদ তার সিদ্ধান্তে কোনো সাধারণীকরণ করেন না।
বাংলাদেশে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর মঙ্গোলয়েড পরিবারের প্রভাব থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনার উল্লেখ করেন তিনি। বিভিন্ন ধারার মানবশ্রেণীর মিলনে দৈহিক বৈশিষ্ট্যে যে মিশ্রপ্রবণতা বাঙালির এক বাস্তবতা, একে তিনি ব্যক্ত করেন। ফলত বাংলাভাষী অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষের মাথার আকৃতি মাঝারি। গোল মাথার এ বৈশিষ্ট্য লম্বা ও গোল মাথা মানুষের মিলনের ফসল। তাহলে দেখা যাচ্ছে মিশ্রণই এখানকার প্রধান বাস্তবতা, অন্তত মাথার বিচারে। ইউরোপীয় চোখ দিয়ে এখানকার মানবধারা বিচারে তার আপত্তি। তিনি লিখেন, ‘আমাদের দেশে মানবধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেকে ইউরোপীয় মানবধারার ধারণাকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। যেটা করা উচিত নয়। তবুও এটা করা হয়েছে। যাতে হয়ে গেছে অর্থ বিভ্রাট। যেমন- যাদের মাথা লম্বা এবং মাথার মধ্যভাগ কিছুটা উঁচু, উত্তর ভারতে এ রকম লোককে বলা হয়েছে নর্ডিক।
কিন্তু নর্ডিকদের মাথার চুল সাধারণত হয় সোনালি এবং চোখের তারার রঙ হয় নীল কিন্তু এদের এই বৈশিষ্ট্য নেই। বাংলাদেশের মানুষকে অনেকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন আলপাইন হিসেবে। কারণ, এদের অনেকের মাথা আলপাইনদের মতো গোল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যা ঠিক ইউরোপীয় মানবধারার সাথে মেলে না।’ এবনে গোলাম সামাদের অনুসন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) কিংবা পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) বিচারের মুখোমুখি দাঁড়ায়। বঙ্কিম বাংলাভাষীদের বিভক্ত করেন চার ভাগে। বিশুদ্ধ আর্যহিন্দু তথা ব্রাহ্মণ, আর্য-অনার্য মিশ্র হিন্দু, আর তৃতীয়টি হলো অনার্য হিন্দু এবং চতুর্থটি হলো বাংলাভাষী মুসলমান। তার কাছে বাংলাভাষী মুসলমান জন্মগতভাবে একটি পৃথক জাতি, নিকৃষ্ট। যাদের মধ্যে আর্যরক্তের লেশমাত্র নেই।
সে কারণেই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের ফুটবল খেলার মাঠে দুই দলের খেলা দেখি : একদল বাঙালি, আরেক দল মুসলমান। আর্যদের মহিমান্বিত করায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কে কার চেয়ে ছিলেন পিছিয়ে? রাজা রামমোহন রায়, (১৭৭২-১৮৩৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২- ১৮৫৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) থেকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) অবধি! অতএব অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই, যখন নেহরু তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে ইংরেজিতে লেখা চিঠিতে বলেন, ‘আর্য কথাটার মানে ভদ্রলোক, উচ্চ-মার্জিত সজ্জন। আর্যরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। আর আজ! আমরা সেই আর্যদের বংশধর হয়েও পরাধীনতার শৃঙ্খলকে গলায় মালা করে পরে আছি।’
কিন্তু আর্যরা তো এখানে এসেছিল দখলদার হয়ে। তারা তো ধ্বংস করেছিল এখানকার উন্নত সভ্যতা। তারা যুদ্ধে ছিল সক্ষম। কিন্তু তা দিয়ে হরপ্পা সভ্যতার উপর চালানো বিনাশের জবাব কী হতে পারে? এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। এবনে সামাদ ঐতিহাসিক সেই সত্যকে মনে করিয়ে দেন। আমাদের দৃষ্টি বারবার ফিরে যায়, সেই দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর দিকে, যারা আর্য ছিল না। বসবাস করত দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চলজুড়ে। খুবই উন্নত ছিল তাদের সভ্যতা। তাদের ছিল নিজস্ব অক্ষর-বত্তেলিও। ছিল লিখিত সাহিত্য। তাদের রক্তধারা বাংলা ও ভারতে এখনো প্রবহমান। তাহলে কিভাবে সত্য হয় নেহরুর সেই বিবরণ, যাতে মনে হয় ভারত যেন কেবলই আর্যদের? কিভাবে সত্য হয় বঙ্কিমের সেই বিভাজন, যা দাবি করে আর্য রক্তই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড? গোলাম সামাদ সেসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকেন। আর্যরক্তকে শ্রেষ্ঠ ধরে বাঙালি মুসলমানের রক্ত নিয়ে যখন আপত্তি, তখন কী জবাব হবে ম্যাক ফারলেন (E.W.E. Macfarlane) এর তত্ত্বের, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে যে জার্মান ইহুদি মহিলা নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ করতে চান, বাঙালি নিম্নবর্ণের হিন্দুর রক্ত আর বাঙালি মুসলমানের রক্ত একই প্রকারের! এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে যান, বাঙালি হিন্দুর নি¤œবর্ণের থেকেই হয়েছে বাঙালি মুসলমানের উদ্ভব। কিন্তু তিনি মাত্র ১২০ জন মুসলমানের রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন।
এ গবেষণায় দুর্বলতা ছিল অনেক গভীর। পরবর্তীকালে দিলীপ কুমার সেনের (D.K. Sen) গবেষণা থেকে দেখা যায়, বাঙালি মুসলমানের রক্ত যত না মেলে বাঙালি হিন্দুর নিম্নবর্ণের সঙ্গে, তার চেয়ে বেশি মেলে উচ্চবর্ণের সঙ্গে। দিলীপ কুমার সেনের গবেষণা অনুসারে, বাঙালি মুসলমান কেবল বাঙালি হিন্দুর নি¤œবর্ণের লোক থেকেই হয়েছে এই মতবাদ স্বীকার্য নয়। আর হিন্দুদের পূর্বে বৌদ্ধগণ যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারও প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। সামাদ দেখান, দক্ষিণ ভারতে জাফর শরীফ নামে এক ব্যক্তি ‘কানন-ই-ইসলাম’ নামে একটি বই লেখেন। পরে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন G. A. Herklot। বইটির নাম দেন Islam in India। ১৯২১ সালে বইটিকে ঢেলে সাজান ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক উইলিয়াম ক্রুক। এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ক্রুক বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুরা মুসলমান হননি, হয়েছিলেন বৌদ্ধরা। তাই বাংলাদেশে (অর্থাৎ তখনকার বাংলা প্রদেশে) মুসলমানের সংখ্যা বেশি। ক্রুকের মতটি গ্রহণ করা হয়েছে ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ওহফরধ বইতে। ১৯৪০-এর দশকে জার্মান গবেষক ম্যাকফারলেন পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলমানের রক্তের গ্রুপ বিশ্লেষণ করে বলেন, তাদের রক্তের গ্রুপের বিভিন্ন হারের সাথে মিলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের রক্তের বিভিন্ন গ্রুপের হার। তাই ধরে নেয়া যায়, বাংলাভাষী মুসলমানদের উদ্ভব হতে পেরেছে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে। কিন্তু এই মত এখন আর আদৃত নয়।
কেননা, নতুন গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের রক্তের গ্রুপের বিভিন্ন হার যত না মিলছে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে তার চেয়ে অধিক মিলছে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে।’ তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানকার বঙ্কিমকথিত তিনটি বাঙালি রক্তধারাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে তার মূল দাবি এমনিতেই খারিজ হয়ে যাচ্ছে যে, বাংলাভাষী মুসলমান আর্যরক্ত বহন করে না এবং তারা বাঙালি নয়। যদিও আর্য রক্তের পবিত্রতার দাবি একটি বর্জনীয় বর্ণবাদ এবং এ দিয়ে বাঙালিত্ব মাপা গুরুতর অবিচার। আর বাঙালি মুসলমান কেবলই স্থানীয় ধর্মান্তরের ফসল নয়। তাদের প্রধান এক অংশ বাইরে থেকে এসেছেন।
এখানে গ্রহণ করে নিয়েছেন স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবন। বাংলা ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মধ্য এশিয়া থেকে আগত ইসলাম প্রচারক এবং যুদ্ধবিজয়ী শাসকদের মহানুভবতার প্রভাবে। এই অঞ্চলে যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ ঘটেছে তাতে মূল অবদান রেখেছেন মুসলমান শাসক ও অমাত্যবর্গ। অতএব সামাদের উপসংহার, ‘বাংলাদেশের জাতিসত্তাকে উপলব্ধি করতে গেলে ইসলামকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর হতে পারে না। ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে এ দেশের জাতিসত্তায়। ইসলামকে বলা চলে এ দেশের জাতিগঠনের বিশেষ উপাদান (Ethno-formative factor)।’
লিখেছেন কবি, গবেষক এবং বহু কিতাবের প্রণেতা মুসা আল হাফিজ। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক নয়া দিগন্তে, ১৩ জুলাই ২০২১।