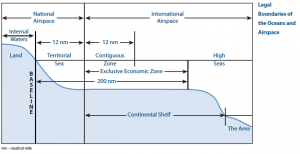গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর দু’টি গতি আছে। একটি হলো নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন বা আহ্নিক গতি। আর অন্যটি হলো পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি। পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি বলতে বোঝায় পৃথিবীর সূর্যকে নিজ কক্ষপথে পরিক্রম করা। পৃথিবীর এই দু’টি গতি চলেছে একসাথে। পৃথিবী গোলাকৃতি। তা নিজ অক্ষের ওপর ঘুরছে বলে হতে পারছে দিন-রাত। অন্য দিকে, পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রম করছে বলে হতে পারছে ঋতু পরিবর্তন। পৃথিবী তার কক্ষপথে সাড়ে ৬২ ডিগ্রি সূর্যের দিকে হেলে তাকে প্রদক্ষিণ করে। তাই হতে পারে দিন-রাতের কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া। হতে পারে ঋতু পরিবর্তন। মানুষ এসব কথা জেনেছে অনেক পরে। এর অনেক আগেই মানুষ শুরু করেছে বছর গণনা। উদ্ভূত হতে পেরেছে সন-তারিখের ধারণা।
প্রাচীন ব্যাবিলনের (বর্তমান ইরাক) পুরোহিতেরা লক্ষ করেছিলেন, রাতের আকাশে কতগুলো নক্ষত্র প্রতি রাতে পশ্চিম দিকে সরে যেতে থাকে এবং একপর্যায়ে তাদের আর দেখা যায় না। তাদের স্থলে দেখা যায় নতুন নক্ষত্রদের। তারাও প্রতি রাতে একইভাবে সরে যেতে থাকে ও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু এসব নক্ষত্রকে বছরের নির্দিষ্ট দিনে দেখা যায় একই জায়গায়। প্রাচীন ব্যাবিলনে এভাবে শুরু হয় নক্ষত্রের অবস্থান দিয়ে বছর গণনার রীতি। প্রাচীন ব্যাবিলন থেকে এভাবে বছর গণনার রীতিনীতি হয় নানা দেশে। এই উপমহাদেশে হিন্দুদের মধ্যে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাদের বলা হতো শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। যাদের প্রধান কাজ ছিল পঞ্জিকা প্রণয়ন। মনে করা হয় যে, এদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন থেকে। আর এরা এই উপমহাদেশের উত্তর ভাগে নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে বছর গণনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বাংলা বার মাসের নাম এসেছে বারটি নক্ষত্রের নাম থেকে। এরা হলো : বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্বভাদ্রপদ, আশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্বফালগুনী ও চিত্রা। এদের নামানুসারে হয়েছে বাংলা মাসের নাম। যথাক্রমে বৈাশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। মার্গশীর্ষ মাসকে বলা হয়েছে অগ্রহায়ণ। কেননা, একসময় বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাসকে ধরা হতো বছর শুরুর মাস। অগ্র অর্থ আগা বা শুরু। আর হায়ণ মানে বছর। বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হতো না। অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম আরম্ভ মাস ধরা হতো। কারণ, এ সময় কাটা হতো আমন বা হৈমন্তিক ধান, যা ছিল বাংলাদেশের প্রধান ফসল। হৈমন্তিক ধান দিয়ে দেয়া হতো রাজার রাজস্ব। সাধারণত এই ফসলের চার ভাগের এক ভাগকে ধরা হতো রাজার প্রাপ্য। বিষয়টি বোঝা দরকার। কেননা, এ দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন উদীচী ও ছায়ানট বলছে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় হলো নববর্ষ উৎসবে। আর এই নববর্ষের দিন হলো পয়লা বৈশাখ।
কিন্তু পয়লা বৈশাখ থেকে চিরকাল বাংলা নববর্ষ শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে একসময় পয়লা অগ্রহায়ণ থেকে। বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড় হয় বৈশাখ মাসে। বাংলাদেশ কৃষকের দেশ। বৈশাখে কৃষক থাকেন আতঙ্কে। বৈশাখ মাস তাই বিবেচিত হতে পারেনি উৎসবের মাস হিসেবে। কিন্তু এখন বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ দাবি করছেন বৈশাখ মাস ছিল এবং এখনো আছে আমাদের উৎসবের মাস হয়ে। কী ইতিহাস, কী ভূগোল, কোনো যুক্তি দিয়েই এদের এই দাবিকে সমর্থন জানানো চলে না। বাংলাদেশে চাঁদের হিসাবে বছর গণনা হয়েছে। চাঁদের কলা ধরে হতে পেরেছে এই হিসাব। চাঁদ যখন একেবারে দেখা যায় না, তখন হয় অমাবস্যা তিথি। আর চাঁদের সবটা যখন আলোয় ভরে ওঠে তখন ধরা হয় পূর্ণিমা তিথি। একে বলে শুক্লাপক্ষ। পূর্ণিমার পরে ১৫টি তিথি ধরে আস্তে আস্তে চাঁদের আলো কমে অমবস্যা হয়। একে বলে কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ ধরে হয় চাঁদের মাস। চাঁদের মাস ধরে গণনা করা হয় চন্দ্রাব্দ। হিন্দুরা পূজাপার্বণ করেছেন চন্দ্রাব্দ ধরে। তারা চেষ্টা করেছেন চন্দ্রাব্দ ও সৌরাব্দের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে। এ জন্য সৌরাব্দ ও চন্দ্রাব্দের মধ্যে যখন এক মাসের ব্যবধান ঘটেছে, তখন তাকে তারা বলেছেন মলমাস। মলমাসকে বাদ দিয়েছেন বছরের হিসাব থেকে। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমান এভাবে চন্দ্রাব্দ ও সৌরাব্দের মধ্যে কোনো সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেননি। তারা তাদের ধর্ম পালন করেছেন হিজরি অনুসারে। হিজরি চন্দ্রাব্দ। কিন্তু কৃষিকর্ম করেছেন সৌরাব্দ তথা বাংলা অব্দ ধরে (সন শব্দটা আরবি থেকে পাওয়া। সন শব্দের ফারসি রূপ হচ্ছে সাল। অব্দ সংস্কৃত শব্দ। অব্দ বলতে বোঝায় বিশেষ পদ্ধতিতে গণিত বছর)। যাকে বলা হয় খ্রিষ্টাব্দ, যা প্রবর্তন করেন পোপ গ্রেগরি ১৩। ইনি পোপ ছিলেন ১৫৭২ থেকে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর প্রবর্তিত খ্রিষ্টাব্দ গণনাকে ইংরেজেরা গ্রহণ করেন ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যদি ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে না পারত, তবে আমাদের দেশে পোপ গ্রেগরি, ১৩ প্রবর্তিত খ্রিষ্টাব্দের প্রচলন হতে পারত না।
বাংলা একাডেমি পোপ গ্রেগরি-১৩ প্রবর্তিত খ্রিষ্টাব্দের সাথে বাংলা অব্দের সমন্বয় করতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। কারণ এটা করা সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলা ১৩৫৮ অব্দের ৮ ফাল্গুন। কিন্তু এখন তা দাঁড়াচ্ছে গ্রেগরি ক্যালেন্ডার ধরলে ৯ ফাল্গুন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ছিল বাংলা ১৩৭৮ অব্দের পয়লা পৌষ। এখন তা গ্রেগরি ক্যালেন্ডারে দাঁড়াচ্ছে ২ পৌষ। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, বাংলা অব্দের সাথে গ্রেগরি ক্যালেন্ডারকে মেলাতে পারব না। তফাৎ তৈরি হবেই। আমাদের উচিত হবে বাংলা অব্দ অনুসারে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা। তাহলে এরকম বিভ্রাট ঘটবে না। আমরা কেন বাংলা অব্দ অনুসারে বাংলার ইতিহাস লিখতে চাচ্ছি না, সেটা একটা প্রশ্ন। খ্রিষ্টাব্দ অনুসারে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা বাঙালিত্বের পরিচয় বহন করছে না। একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগে, তা হলো এ দেশে অনেক লোক আছেন, যারা খ্রিষ্টাব্দকে মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষ আর হিজরিকে মনে করেন ইসলামি। তাই এটাকে বাদ দেয়া উচিত। তবে আমাদের পত্রপত্রিকায় হিজরি, বঙ্গাব্দ এবং খ্রিষ্টাব্দের উল্লেখ থাকতে দেখা যায় প্রতিদিন।
এবারের পয়লা বৈশাখ অন্য বছরের মতো জমজমাট হলো না। পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা হলো পুলিশ পাহারায়। সর্বত্র বিরাজ করছিল একটা ভীতিবিহ্বলতা। কেননা, মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্যে থাকে একটা হিন্দুয়ানি ভাব। মঙ্গল শোভাযাত্রা করা হয় এই ভেবে যে, বছরটা হবে মঙ্গলময়। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে একটি পূজার মনোভাব। যেটাকে বাংলাদেশের মুসলিম মানস এখন আর প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হচ্ছেন না। তারা চাচ্ছেন এটাকে বন্ধ করতে। তাই মঙ্গল শোভাযাত্রা হতে হচ্ছে পুলিশ পাহারায়। সরকার অবশ্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা করতে হবে, এই নির্দেশনা দিয়েছিল। কিন্তু কেন সরকার থেকে জোর করে মঙ্গল শোভাযাত্রা করার নির্দেশ থাকবে, সেটা নিয়ে জনমনে সৃষ্টি হতে পেরেছে ক্ষোভ। এই ক্ষোভ এর আগে হতে দেখা যায়নি। পয়লা বৈশাখ আর থাকছে না উৎসবের দিন। তা হয়ে উঠতে চাচ্ছে এক বিশেষ ধরনের রাজনীতির দিন। কিন্তু এই রাজনীতি দেশকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে রক্তক্ষয়ের পথে বলেই মনে হয়।
নববর্ষের উৎসবে দু’টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছে। একটি হলো উদীচী আর একটি ছায়ানট। উদীচী নামটা, এরা কেন গ্রহণ করেছেন, তা আমার জানা নেই। কেননা, উদীচী বলতে বোঝাত এই উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। যার মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে না। তাই বাংলাদেশের একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কেন উদীচী নাম গ্রহণ করল, সেটা নিয়েও দেখা দেয় প্রশ্ন। সাধারণত মনে করা হয় যে, উদীচী মণ্ডলের কথিত ভাষাকে সংস্কার করে উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষার। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখেন পানিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। পানিনি ছিলেন সালাতুরের অধিবাসী, যা এখন পড়েছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আটক জেলায়। জানি না, উদীচীর ভক্তরা এ সম্বন্ধে অবগত কি না। যত দূর জানি উদীচীর ভক্তরা নববর্ষে চালু করেছিলেন ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়া। কিন্তু এই বছর ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা খেতে দেখা গেল না সংস্কৃতিমনাদের। বাংলাদেশের মানুষ অতীতে পান্তা ভাত খেয়েছেন এবং এখন তারা পান্তা ভাত খান। কিন্তু কেবল পান্তা ভাতই তাদের খাদ্য-সংস্কৃতির পরিচয়বহ নয়। এ দেশের মানুষ চালের গুঁড়া দিয়ে বানিয়েছেন বহু প্রকার পিঠাপুলি, যা তারা খেয়েছেন আনন্দসহকারে। তারা দুধ দিয়ে রান্না করেছেন চালের পায়েশ। বাংলাদেশের মুসলমানেরা প্রধানত ভাত খেলেও তাদের মধ্যে গমের ময়দার রুটি খাওয়ার চল ছিল। এ ছাড়া তারা গমের ময়দা দিয়ে বানিয়েছেন সেমাই। তাদের মধ্যে ছিল সেমাই খাবার চল। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যা ছিল না। বাঙালি মুসলমান পাখির গোশত খেয়েছেন প্রচুর। এ দেশে শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে প্রচুর বুনোহাঁস উড়ে এসেছে। মুসলমানেরা এদের জাল পেতে ধরে গোশত রান্না করে খেয়েছেন। মুসলমান সমাজে ছিল এবং এখনো আছে নানা ধরনের গোশত রান্নার পদ্ধতি। তারা কখনোই কেবল পান্তা ভাত খাবার কথা চিন্তা করেননি।
খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্পেন দেশ থেকে খ্রিষ্টান মিশনারি পরিব্রাজক মানরিক এসেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীর এক জায়গায় লিখেছেন, তিনি গৌড়ের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে খানা খেতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তাকে এত পদ খেতে দেয়া হয়েছিল যে, তা খেয়ে শেষ করতে তার লেগেছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা। হিন্দুশাস্ত্রে খাদ্য সম্পর্কে কী উপদেশ দেয়া হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আল কুরআনে বলা হয়েছে, সুস্বাদু খাবার খেতে (সূরা ২: ১৭২)। মুসলমানেরা সব দেশেই চেয়েছেন সুস্বাদু খাদ্য রান্না করে খেতে। মুসলমানেরা সব দেশেই গমের ময়দা দিয়ে বানিয়েছেন নানা রকম হালুয়া। যার একটা প্রভাব বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও ছিল এবং এখনো আছে। অথচ উদীচী বাঙালি সংস্কৃতি বলতে কেবলই বোঝাতে চেয়েছে, পান্তা ভাত খাওয়াকে। বাংলাদেশের মানুষ পান-সুপারি প্রচুর খেয়েছেন। অতিথিকে আপ্যায়ন করেছেন পান-সুপারি দিয়ে। কিন্তু পান-সুপারি উদীচীর কাছে হতে পারেনি বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে। উদীচীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেছে খুবই সীমিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের খাদ্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।
যত দূর জানি ছায়ানট একটা রাগিণীর নাম। ছায়ানটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। জানি না, রবীন্দ্রনাথের কোনো গানের সুরে ছায়ানট রাগিণীর কোনো প্রভাব আছে কি না। তবে সুর বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের গানে আছে মধ্য বাংলার বাউল সুরের বিশেষ প্রভাব। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কেবল বাউল সুরই যে আছে, তা নয়। আছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি প্রভৃতি সুর। কিন্তু ছায়ানট মনে করে বাংলা গানের পরিচয় ফুটে উঠেছে কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই মধ্যে। যেটাকে সমর্থন দেয়া যায় না।
ছায়ানটের আরেকটি দাবি, আমাদের অনুসরণ করতে হবে রবীন্দ্র-দর্শনকে। কেননা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক। যেটাকেও ধরা চলে অতি কথন হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথেষ্ট অত্যাচারী জমিদার। কাঙাল হরিনাথ ঠাকুর পরিবারের অত্যাচারের কথা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের পিতা গুণ্ডা নিযুক্ত করেছিলেন কাঙাল হরিনাথকে খুন করে ফেলার জন্য। কাঙাল হরিনাথ আমাদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন, কেননা কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে বাংলা গদ্য লিখতে শেখেন বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা এসেছিল কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নয়। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় না অসাম্প্রদায়িক। নওগাঁর পতিসরে ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারি। এখানে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ির ঠিক পেছনে আছে একটা বিড়াট দিঘি। এই দিঘিতে কোনো মুসলমানকে স্নান করতে দেয়া হতো না, দিঘির পানি অপবিত্র হবে বিধায়। এসব কথা আমি নিজে শুনেছি পতিসরের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে। আমি তাই মানতে পারি না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক।
একসময় রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে কোনো মুসলমান ছাত্র পড়তে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়ার জন্য হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের কাছে চেয়েছিলেন চাঁদা। নিজাম বাহাদুর তাকে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সে দিন এক লাখ টাকা ছিল অনেক টাকা। এ সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু হাতেগোনা মুসলমান ছাত্র পড়বার ব্যবস্থা করেন শান্তি নিকেতন ও বিশ্বভারতীতে। এসব হাতেগোনা ছাত্রদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী পেতে পেরেছেন বিশেষ সাহিত্য-খ্যাতি। রবীন্দ্রনাথ তার প্রজাদের শিক্ষার জন্য পতিসরে কোনো বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন না। পতিসরে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন উচ্চ মন-মানসিকতার পরিচয়। তাই ছায়ানটের বক্তব্য আমাদের কাছে মনে হয় না গ্রহণযোগ্য। এবারে পয়লা বৈশাখে ছায়ানটকেও খুব উচ্চ কণ্ঠ হতে দেখা গেল না।
বাংলা সাল গণনা করা নিয়ে অনেক মত প্রচলিত আছে। একটি মত হলো, আকবর বাদশা এই সালের প্রবর্তন করেন। তিনি এই সালের প্রবর্তন করেন হিজরি ৯৬২-৬৩তে পারস্যে প্রচলিত সৌর সাল অনুসারে। এই সাল গণনা করা হতো প্রাচীন ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু বাংলা সালের নাম এবং গণনা পদ্ধতিতে আছে কিছু পার্থক্য। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, আকবরের প্রবর্তিত সাল আর বাংলা অব্দ হলো একই। তবে যেহেতু এই দুই সাল গণনার ভিত্তি হলো প্রাচীন ব্যাবিলনের সৌর সাল গণনার পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, তাই এই দুই সাল গণনার পদ্ধতিতে থাকতে দেখা যায় যথেষ্ট ঐক্য। বাংলা সাল নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। আমরা যার মধ্যে যেতে চাই না। আমাদের প্রবন্ধে বাংলা সাল নিয়ে যা আলোচনা করলাম, তা হলো একটা খুব মোটামুটি ধারণামাত্র। যেহেতু বাংলা সালের সাথে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বিশেষ ধরনের রাজনীতিকে, তাই আমাদের এই আলোচনা করা।
প্রকাশিত দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২১ এপ্রিল ২০১৭ এ।