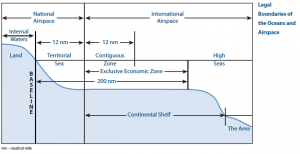হিন্দু জনসমাজ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ‘বর্ণ’ কথাটার অর্থ হলো ‘রং’। হিন্দুধর্মে বলা হয়, মানুষ হলো চার রঙের। এরা হলো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণদের গায়ের রং হলো ফর্সা, ক্ষত্রিয়দের গায়ের রং হলো রক্তাভ, বৈশ্যদের গায়ের রং হলো হরিদ্রাভ আর শূদ্ররা হলো কৃষ্ণকায়। এ কথা বলা হয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।
ব্রাহ্মণদের কাজ হলো পূজা-অর্চনা ও জ্ঞান চর্চা করা। ক্ষত্রিয়দের কাজ হলো যুদ্ধ করে ক্ষেত্র রক্ষা করা। বৈশ্যদের জীবিকার উপায় হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আর শূদ্রদের জীবিকার উপায় হলো কেবলই কায়িক পরিশ্রম। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে আছে অস্পৃশ্যতার ধারণা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে ধরা হয় উচ্চবর্ণ। আর শূদ্রকে ধরা হয় নি¤œবর্ণ। তাদের করা হয় বিশেষভাবে ঘৃণা। উচ্চবর্ণের লোকেরা শূদ্রদের সাথে ওঠা-বসা, আহার বিহার করেন না। এ হলো হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। ধরা হয় গোড়ায় ছিল মাত্র চারটি বর্ণ।
কিন্তু পরে শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে হিন্দু জনসমাজে সৃষ্টি হতে পেরেছে অজস্র বর্ণ। আর তাকে নির্ভর করে সৃষ্টি হতে পেরেছে বর্ণবৈষম্য। বর্ণবৈষম্যের তীব্রতা ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে কিছুটা কমে গেলেও বহু অঞ্চলেই কমে যায়নি। বর্ণবৈষম্যকে চলতি কথায় উত্তর ভারতে বলা হয়, জাত-পাতের বিরোধ। জাত-পাতের বিরোধ ভারতের রাজনীতিতে হয়ে আছে একটা উল্লেখ্য বিষয়। ভারতে সবচেয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের এখন হিন্দিতে বলে ‘দলিত’। দলিতদের ছোঁয়া লাগলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের দেহ অপবিত্র হয়। তাদের বিশেষভাবে স্নান করে হতে হয় পবিত্র।
ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও তার স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ গিয়েছিলেন উড়িষ্যার পুরি শহরের বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরে পূজা দিতে (১৮ মার্চ ২০১৮)। কিন্তু যেহেতু রামনাথ কোবিন্দ ও তার স্ত্রী সবিতা কোবিন্দ হলেন দলিত সমাজের লোক, তাই তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না জগন্নাথ মন্দিরে। করা হয় ভয়ঙ্করভাবে অপমান। এ হলো আজকের ভারতের হিন্দু বর্ণবাদের চিত্র। হিন্দুরা সাধারণভাবে সব মুসলমানকে ভাবেন অশূচি। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মরক্কো থেকে ইবনে বতুতা এসেছিলেন উত্তর ভারত ভ্রমণে। তিনি তখনকার বাংলাদেশেও এসেছিলেন। ইবনে বতুতা তার ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, হিন্দুরা তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিককে পান করবার জন্য পানি চাইলে তা দেয় না। কারণ, তারা ভাবেন মুসলমানেরা হলেন অশূচি। তাদের পানি দিলে বাসন অপবিত্র হবে।
আমাদের দেশে অনেক বুদ্ধিজীবী এখন উপলব্ধি করতে পারেন না, কেন কী কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হতে পেরেছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হতে পারার একটা বড় কারণ হলো হিন্দুরা মুসলমানকে ভাবেন ম্লেচ্ছ বা অশূচি। এই বিশেষ ঘৃণা কাজ করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের মূলে, ব্রিটিশ শাসনামলে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটিশ শাসনামলে বর্ণবাদ সাধারণভাবেই হিন্দু সমাজে বিশেষ প্রাধান্য পায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার রচিত ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’-এর তৃতীয় খণ্ডের এক জায়গায় বলেছেন, ‘অপ্রিয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যে কেবল সৈয়দ আহম্মদ ও জিন্নার অবদান আছে তাহা নহে, মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে হিন্দুদিগের চিরন্তন মনোভাবও ইহার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী।’
দলিত সমাজের লোক ছিলেন ড. আম্বেদকর। আম্বেদকর করেছিলেন ভারতের সংবিধানের মুসাবিদা। তিনি ১৯৫০ সালে তার অনুসারীদের নিয়ে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেন বৌদ্ধ ধর্ম। এসব বৌদ্ধকে ভারতে বলা হয় নওবৌদ্ধ। ১৯৫০ সালে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লাখ। কিন্তু বৌদ্ধ হওয়ার পরেও নওবৌদ্ধরা হিন্দুদের কাছে হয়ে আছেন অস্পৃশ্য। তাদের অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। ভারতে
১৯৫৫ সালে প্রবর্তিত হয় হিন্দু-বিবাহ আইন। এতে বলা হয়েছে, যারা মুসলমান নন, খ্রিষ্টান নন, ইহুদি নন এবং অগ্নিপূজারী পার্সিক নন, ভারতের এ রকম সব নাগরিককেই ধরা হবে হিন্দু। কিন্তু শিখরা এখন নিজেদের হিন্দু ধরতে রাজি হচ্ছেন না। ১৯৪৭ সালে শিখরা হিন্দুদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। সাবেক পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাব। পশ্চিম পাঞ্জাব পড়েছিল পাকিস্তানে আর পূর্ব পাঞ্জাব পড়েছিল ভারতে। কিন্তু ১৯৬৬ সালে শিখরা দাবি করেন পৃথক পাঞ্জাব প্রদেশ। ফলে সৃষ্টি হয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশ। পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয় শিখদের নিয়ে। এর ভাষা হয় গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত পাঞ্জাবি। অন্য দিকে হরিয়ানা প্রদেশের ভাষা হয় নাগরি অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দি।
ব্রিটিশ শাসনামলে গোটা পাঞ্জাব প্রদেশেই একসময় ছিল উর্দু ভাষার বিশেষ প্রাধান্য। এখনও বহু লোক সেখানে যথেষ্ট সহজে উর্দু বোঝেন। ১৯৮৪ সালে শিখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইন্দিরা গান্ধী শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে সমর্থ হন। শিখদের সাথে ভারতীয় সৈন্যের যুদ্ধ চলেছিল ১৯৮৪ সালের ১ থেকে ৮ জুন পর্যন্ত। যাকে ভারতীয় সৈন্যরা নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন ব্লুস্টার’। এর ফলে অমৃতসরের শিখদের বিখ্যাত ধর্ম-মন্দির ধ্বংস হয়, যা নির্মাণ করা হয় আবার নতুন করে। দু’জন শিখ দেহরক্ষী দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীকে তার সরকারি ভবনের আঙিনায় ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪ গুলি করে হত্যা করেন। শিখ স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আগামীতে তা আবার উদ্দীপ্ত হতেই পারে। শিখরা একসময় ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর শতকরা ৩০ ভাগ; কিন্তু এখন আর তাদের আগের মতো সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হচ্ছে না।
তাদের সংখ্যা সেনাবাহিনীতে শতকরা দশ ভাগের নিচে নেমে গেছে। শিখরা একটি ধর্ম সম্প্রদায়। তারা নিরাকার এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং তারা হিন্দুদের মতো বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী নন। আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, ধর্ম রাজনীতির অংশ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ধর্ম রাজনীতিতে নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এখনো করছে। ভারতের রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ থেকে মিলছে যার বিশেষ প্রমাণ।
ভারতে এখন ক্ষমতায় এসেছে বিজিপি দল। বিজিপি বলছে, তারা হলো হিন্দুত্ববাদী। কিন্তু হিন্দু ধর্মের একটা বিরাট অংশজুড়ে আছে বর্ণাশ্রমের ধারণা। হিন্দুত্বের ওপর গুরুত্ব দেয়ার একটা অর্থ দাঁড়াবে ভারতে বিভিন্ন বর্ণভুক্ত মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত না কমে, বেড়ে যাওয়া। ভারতের রাজনৈতিক জটিলতা না কমে আরো বেড়ে যেতেই থাকবে।
১৯৪৭ সালের আগে ব্রিটিশ শাসিত বাংলা প্রদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলতে বোঝাত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকে। কায়স্থ বলতে বোঝাত পত্র লেখক, দলিল লেখক ও হিসাব রক্ষকদের। বৈদ্য বলতে বোঝাত চিকিৎসকদের। কর্ম বিভাজনের দিক থেকে এসব ছিল তাদের জাত-ব্যবসা। নিম্নবর্ণের হিন্দু বলতে বোঝাত কৈবর্ত (ধীবর), রাজবংশী ও নমশূদ্রদের। রাজবংশীরা প্রধানত ছিলেন কৃষিজীবী। কিন্তু মানবধারার দিক থেকে তারা হলেন মঙ্গলীয়। নমশূদ্রদের জীবিকার উপায় ছিল কৃষি ও মাঝিমাল্লা হওয়া। এদের চেহারার সাথে কিছু সাদৃশ্য আছে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের। এদের গায়ের রঙ অন্যদের তুলনায় অনেক কালো। এরা হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে গণ্য হতেন সর্বনিম্ন বর্ণ হিসাবে।
পাকিস্তান হওয়ার পর তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে দলে দলে উচ্চবর্ণের হিন্দু চলে যান ভারতে। পূর্ববঙ্গে থাকেন প্রধানত নমশূদ্ররা। বর্তমান বাংলাদেশে নমশূদ্ররা আগের মতো আর অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন না। কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছেন। হিন্দু ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ হলো ভগবত গীতা। এতে বলা হয়েছে, সব মানুষ সমান নয়। উচ্চবর্ণের মানুষ ধী ও স্মৃতিশক্তিতে অন্যদের চেয়ে উন্নত। উন্নত কর্মতৎপরতায়, যা বর্তায় বংশ পরম্পরায়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষ গড়ে তুলেছে সভ্যতা। সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে। সব জনসমাজ যে তাদের উন্নতিকে ধরে রাখতে পেরেছে, তা নয়। বড়রা ছোট হয়েছেন, ছোটরা বড় হয়েছেন। এক যুগের ইতিহাসের ঐশ্বর্য পরিণত হয়েছে আরেক যুগের আবর্জনায়।