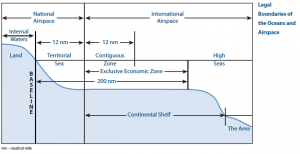প্রাচীন যুগের রাজ্য শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি বৌদ্ধ জাতক থেকে। ‘জাতক’ বলতে বোঝায় গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী। মনে করা হয়, গৌতম বুদ্ধ ৫৫০ বার জন্মেছিলেন, গৌতম বুদ্ধ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার আগে। ধারণা করা হয়, জাতকগুলোর রচনাকাল হলো ৩০০ খ্রি.পূর্বাব্দের কাছাকাছি। আর তাতে যে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তখনকার সময়ের দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাস্তবতা।
অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের একটি অংশ পড়ে এই বর্ণনার মধ্যে। যদিও বাংলাদেশ নামটা এতে স্থান পায়নি। সে সময় রাজা বলতে বোঝাত একটা রাজ্যের, যা গঠিত হতো কতগুলো গ্রাম নিয়ে, সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে। রাজার ছেলেই যে কেবল বংশপরম্পরায় এসব রাজত্বে রাজত্ব করতেন, তা নয়। রাজা অনেক সময়ই হতেন গণনির্বাচিত। ‘গণ’ বলতে বোঝায় যা গণনা করা চলে। জনসমষ্টিকেই গণনা করা যায়। গণের ভোটে এসব রাজা নির্বাচিত হতেন বলে, এই সব রাজ্যকে বলা হতো গণরাজ্য।
গৌতম বুদ্ধের পিতা সুদ্ধোধন ছিলেন বর্তমান নেপালের লুম্বিনি অঞ্চলের রাজা। লুম্বিনী ছিল একটি গণরাজ্য; কিন্তু ক্রমে সর্বত্রই রাজার ছেলে রাজা হওয়া প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। কখনো রাজা যদি পীড়ক হয়ে উঠতেন, তবে প্রজারা বিদ্রোহ করত। বিদ্রোহে জয়ী হলে পুরনো রাজার জায়গায় প্রজারা নতুন কাউকে মেনে নিত রাজা বা সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে। এই ছিল সাধারণ রাষ্ট্রনীতির ধরন। রাজা মন্ত্রী বেছে নিতেন। তিনি এটা বেছে নিতেন তার নিজের পছন্দ অনুসারে।
এদের হতে হতো না কোনো আইনসভার নির্বাচিত ব্যক্তি। তবে প্রাচীন যুগেও সভা ও সমিতি বলে দুটো শব্দ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন ভাষায় ছিল। মানুষ সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সমাজজীবনে কোনো গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে। সমিতি গড়েছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে চেষ্টার মাধ্যমে কার্যকর করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ সমাজে বিরাজমান ছিল বেশ কিছুটা গণতান্ত্রিক চেতনা। কেবল রাজাই যে সব কিছু করতেন এমন নয়। জনমতের একটা চাপ তার ওপরও কাজ করত।
গ্রামগুলোকে দেখাশোনা করতেন গ্রামরক্ষক। গ্রামরক্ষক প্রথমে নির্বাচিত হতেন, কিন্তু পরে তিনি হতে থাকেন রাজার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত। তবে তিনি যদি অত্যাচারী হতেন অথবা অসাধু হতেন তবে গ্রাম্যসমাজ তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করত। জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়, গ্রামরক্ষককে প্রহার করে গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রাম ছাড়া করার কথা। প্রজারা রাজাকে খাজনা দিত ফসলের মাধ্যমে। সাধারণত একজন কৃষকের জমিতে যা ফসল হতো তার চার ভাগের এক ভাগ ছিল রাজার প্রাপ্য। রাজা এই খাজনা দিয়ে কেবল নিজের ভরণপোষণ করতেন না; করতেন পথঘাট নির্মাণ ও সেচের জন্য খাল খনন এবং আরো নানাবিধ পূর্তকর্ম।
বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখি, প্রজারা প্রাচীন যুগে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে করেছেন বিদ্রোহ। নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় ধীবরদিঘি নামে একটি বিরাট দিঘি আছে। এই দিঘির মধ্য ভাগে আছে প্রায় ১২ মিটার উঁচু ও ১২০ মিটার ব্যাসযুক্ত স্তম্ভ। স্তম্ভটিকে বলা হয় ধীবরস্তম্ভ। এটিকে স্থাপন করা হয়েছিল একটি বিশেষ যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য।
দিব্বক ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা। তার নেতৃত্বে প্রজারা বিদ্রোহ করেছিল পাল বংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে। কেননা, মহীপাল হয়ে উঠেছিলেন খুবই অত্যাচারী। দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। প্রজারা দিব্বককে করেন রাজা। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষ অতীতে রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিতে চায়নি। করেছে বিদ্রোহ। যার একটি স্মৃতি এখন বহন করে চলেছে ধীবরদিঘির মধ্যে স্থাপিত এই বিরাট প্রস্তর (গ্রানাইট) স্তম্ভ। অতদিন আগে অত বিরাট স্তম্ভটিকে মাটিতে স্থাপন করে দিঘিটি খনন করতে যে কৌশলের প্রয়োজন হয়েছিল মানুষ সে সময় তা জানত। যেটাও বিস্মিত হওয়ার মতো।
বাংলাদেশ এখন একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। একসময় মনে করা হতো বাংলাদেশে দলে দলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে নমশূদ্ররা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে হতে পেরেছে মুসলমানপ্রাধান্য; কিন্তু এখন আর এই মতটি আগের মতো আদৃত নয়। এখন মনে করা হয় হিন্দুরা নয় বাংলাদেশে দলে দলে বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হতে পেরেছে মুসলিমপ্রাধান্য। যে রকম হতে পেরেছে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে।
খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সুমাত্রা দ্বীপে মেনাংকাবু নামক জায়গায় একটি মুসলিম সালতানাতের উদ্ভব হয়। এখান থেকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে। মেনাংকাবুর ইতিহাস এখনো যথেষ্ট জানা যায় না। তবে পূর্ববাংলার বৌদ্ধরা সুমাত্রা দ্বীপে যথেষ্ট ব্যবসাবাণিজ্য করতে যেতেন বলে জানা যায়। আর তাই ধরে নেয়া যায়, তাদের ওপরও পড়তে পেরেছিল ইসলামের প্রভাব। বাংলাদেশের তুর্কি মুসলিম অভিযান আরম্ভ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এখন মনে করা হয় তুর্কি মুসলিম অভিযানের আগেই এ দেশের অনেক অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল।
বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে। যে সময়টাকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী আমল (১৩৩৮-১৫৭৬ খ্রি.), সে সময়কার মসজিদগুলো করা হয়েছে কতকটা ‘বৌদ্ধ-চৈত্য’র মতো করে। ‘চৈত্য’ বলতে বোঝায় বৌদ্ধমঠের প্রার্থনা কক্ষকে। যেখানে শ্রমণরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন। সুলতানী আমলের মসজিদের গম্বুজগুলো করা হয়েছে কতকটা বৌদ্ধস্তূপের মতো করে। দেখে মনে হয় কতকটা উল্টানো বাটির মতো। হিন্দু মন্দিরের সাথে মসজিদের স্থাপত্যের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। হিন্দু মন্দিরের প্রধান কোঠা বা গর্ভগৃহ যেখানে দেবি বা দেবতার মূর্তি থাকে তা হয় অত্যন্ত ছোট।
হিন্দু পূজার্থীরা দেবতা বা দেবীর মূর্তি দর্শন করে প্রণাম করেন গর্ভগৃহের বাইরে থেকে। তারা মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ করেন না। মূর্তিপূজা করেন কেবল পুরোহিতেরাই। গর্ভগৃহের সাথে যুক্ত চণ্ডীমণ্ডবে জড়ো হন অনেক মানুষ। সেখানে হতে পারে নৃত্যগীত, হতে পারে ধর্মীয় উৎসব; কিন্তু মুসলমান মসজিদে সবাই সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে। এতে প্রকাশ পায় না কোনো উদ্যমতা অথবা বিশৃঙ্খলা। সুলতানী আমলে সব মসজিদের সাথে আছে মেয়েদের পৃথকভাবে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা। সুলতানী আমলে মেয়েরা মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন, তাতে কোনো বাধা ছিল না। কুরআন শরীফে সমবেতভাবে ইবাদত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (সূরা ২ : আয়াত ৪৩)।
মন্দির হিন্দু সমাজজীবনে যে প্রভাব রেখেছে তুলনামূলকভাবে মসজিদ মুসলমান সমাজজীবনে রেখেছে সে তুলনায় অনেক গভীর প্রভাব। মসজিদ কেবল প্রার্থনা স্থান হয়ে থাকেনি, তাকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মসজিদ হয়েছে বিচারালয়, গ্রাম্য সালিসকেন্দ্র। মসজিদে মুসলমান পথিক রাতে এসে ঘুমিয়েছেন নিরাপদে। হিন্দু মন্দিরে যা সম্ভব ছিল না। মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মুসলিম সমাজজীবন। মুসলিম বিচারব্যবস্থা, সমাজজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা।
সে যুগে মুসলিম ছেলেমেয়েরা একসাথে ওস্তাদের কাছে এসে কুরআন পাঠ করেছে। অর্থাৎ মসজিদে ছিল সহশিক্ষার ব্যবস্থা। এখন যেমন সহশিক্ষার ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়, অতীতে তা তোলা হয়নি। সুলতানী আমলে রাজ্য শাসন করেছেন সুলতানেরা। ‘সুলতান’ শব্দটা আরবি। শব্দগত অর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বাংলাদেশের সুলতানেরা বলতেন, তারা ক্ষমতা লাভ করেছেন বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে। তারা সুলতান হয়ে বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে আনতেন তাদের অনুমোদন। সুলতানের ছেলেই যে সুলতান হতেন এমন নয়। বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহর পিতা সুলতান ছিলেন না। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যাকে সুলতান বলে মেনে নিতেন তিনি সুলতানের পুত্র না হলেও হতে পারতেন সুলতান। সব সুলতানকে অবশ্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমর্থন পেতে হতো। অর্থাৎ সুলতানী আমলে এক ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। যাকে বলা যেতে পারে অভিজাত গণতন্ত্র।
বাবর তার আত্মজীবনীতে হুসেন শাহর পুত্র নসরত শাহকে উল্লেখ করেছেন নসরাত শাহ বাঙালি হিসেবে। বাংলাদেশের কোনো রাজা অথবা সুলতান এভাবে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত হননি। বাবর নসরত শাহকে খুবই প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, তিনি তার চৌদ্দটি ভাইকে মেরে ফেলেননি। অথবা অন্ধ করেও দেননি। তিনি তার ভাইদের প্রদান করেন ভাতা। মোগল আমলে কোনো ধরনের গণতন্ত্র থাকেনি। বাংলাদেশে মোগল শাসন আমল অনেক পরিমাণে বিবেচিত হয়েছে বিদেশী শাসন হিসেবে। মোগল শাসন আমলে বাংলাদেশে বারো ভূঁইয়ারা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে করেছেন বিদ্রোহ। বারো ভূঁইয়ার মধ্যে ঈসা খাঁর নাম এখনো যথেষ্ট খ্যাত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে ১৭৬০ সালের কাছাকাছি থেকে বিলাতের অর্থনীতিতে আরম্ভ হয়, যাকে বলে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)। বিলাতের কলে সস্তায় তৈরি হতে আরম্ভ করল কার্পাস তুলার কাপড়। বিলাতের এই কাপড় আমাদের দেশে বাজার ভরে ফেলল। আমাদের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের হলো প্রচণ্ড ক্ষতি। যেহেতু দেশ শাসিত হচ্ছিল ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানির দ্বারা, তাই কাপড়ের ওপর কোনো আমদানি শুল্ক আরোপ করে আমাদের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।
এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার তন্তুবায় হয়ে পড়েন কর্মহীন। তারা খেটে খেতে শুরু করেন ক্ষেতে-খামারে। এ সময় নীলকর সাহেবেরা এসে এ দেশে শুরু করেন নীল চাষ। এদের অত্যাচারে কৃষকেরা হন জর্জরিত। এ ছাড়া সৃষ্টি হয় এক নতুন জমিদার শ্রেণী। সব মিলিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কষ্ট পৌঁছায় চরমে।
ইসলামী পরিভাষায় ফরজ মানে যা অবশ্য পালনীয়। ফরজের বহুবচন ফারায়েজ। হাজী শরীয়তুল্লাহ আরম্ভ করেন ফরায়েজি আন্দোলন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন (ডাকনাম দুদু মিয়া) হন ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। ফরায়েজিরা জমিদারবাড়ি লুট করেন, আগুন দিয়ে পোড়ান নীলকরদের কুঠিবাড়ি। এই হলো বাংলাদেশের ইসলামের ঐতিহ্য। ইসলামে জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই ফরজ। ইসলাম একটি হিংসাশ্রয়ী ধর্ম নয়। হাদিসে বলা হয়েছে : বিষধর সর্পকেও কষ্ট না দিয়ে বধ করতে। ইসলাম মানুষের বিচার-বুদ্ধিতে আস্থা রাখতে বলে। হাদিসে তাই বলা হয়েছে : আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার উটকে শক্ত করে বাঁধতে ভুলবে না। ইসলাম একটি প্রচলিত দক্ষিণপন্থী ধর্ম নয়। ইসলামের নবী সা: তাই তাঁর বিদায় হজের বক্তৃতায় বলেছেন, শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে তার মজুরি পরিশোধ করে দিতে। আল কুরআনে বলা হয়েছে : দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে আহার্য প্রদান করতে। দুর্ভাগ্যকবলিত মানুষকে সাহায্য করতে। অনাথ শিশুকে প্রতিপূরণ করতে।
বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হলো। ভোট নিয়ে যথেষ্ট কথা হচ্ছে। কথা উঠছে ভোটে ঘটেছে প্রচুর অনিয়ম। নৌকা সমর্থক অনেকে ভোট দিতে গিয়ে দেখেন তাদের ভোটও আগে কেউ দিয়ে গেছেন। দুপুর ১২টার মধ্যেই হয়ে যায় ভোট দান সম্পন্ন। বহু লোক ভোট দিতে পারেননি। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট দাবি করছে পুনঃনির্বাচনের; কিন্তু আমাদের সংবিধানে পুনঃনির্বাচনের কোনো বিধান নেই। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের বিধান আছে। আওয়ামী লীগ সরকার যদি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন দেয় এবং করে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, আমার মনে হয়, এ দেশের রাজনীতিতে জঙ্গি তৎপরতা আত্মপ্রকাশ করবে না।
বলা হচ্ছে, এ দেশে জামায়াতে ইসলামী একটি মুসলিম জঙ্গিবাদী দল। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ জামায়াতে ইসলামী ধানের শীষে যোগ দিয়ে একাদশ নির্বাচন করেছে। জঙ্গিবাদ প্রদর্শন করেননি। আমরা দেখে দুঃখিত হচ্ছি যে, ড. কামাল হোসেন ঐক্যফ্রন্টে থেকে অহেতুক জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে টানাটানি করছেন। এর ফলে ঐক্যফ্রন্ট ভেঙে যেতেও পারে। যাতে লাভবান হবে বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ।
বিএনপির সাথে জামায়াতের ঐক্য হতে পেরেছে বিশেষ কারণে। জামায়াত ও বিএনপি উভয়ে ভারতের আধিপত্যবাদবিরোধী। উভয়ে মোটামুটি বিশ্বাস করে ইসলামী মূল্যবোধে। বিশেষ করে ইসলামের মানবতন্ত্রী দিকটির ওপর এই দুই দলই আরোপ করতে চায় বিশেষ গুরুত্ব। এটাও সত্য- আওয়ামী লীগ জামায়াতের সাথে হাত মিলিয়ে ১৯৯৬ সালে করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন। তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ জামায়াতকে বলেনি একটি জঙ্গি ইসলামী দল। অথবা বলেনি স্বাধীনতার শত্রু।
কিন্তু এখন সেই জামায়াতকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছে সেভাবেই। জামায়াত একটি সাইনবোর্ডসর্বস্ব দল নয়। যেমন সাইনবোর্ডসর্বস্ব দল হচ্ছে ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম। তিনি যদি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে চলে যেতে চান তবে অবশ্যই চলে যেতে পারেন। আমার মনে হয় না তাতে ঐক্যফ্রন্ট বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটি ঐক্যজোটে যোগ দিয়েই কথাবার্তা বলা উচিত এমনভাবে যে, ঐক্যজোট ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; কিন্তু তিনি তা করছেন না। তাকে নিয়েও আছে আরো কিছু বিতর্ক।