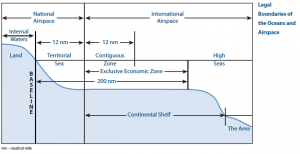বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চলেছে এক ধরনের পুজা। এদেশে রবীন্দ্র সাহিত্যের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি আলোচিত হয়ে থাকেন। প্রমাণ করার চেষ্টা চলেছে, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উৎস হলেন রবীন্দ্রনাথ। একথা ঠিক, পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল রবীন্দ্র সাহিত্য পঠন ও পাঠনের ওপর। এদেশের মানুষ করেছিল যার প্রতিবাদ। কিন্তু তাই বলে বলা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। কারণ, রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন কিছু নেই যে, তা বিশেষভাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে একটা পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। আমাদের জাতীয় চেতনার অন্যতম উৎস হলো ভাষা। রবীন্দ্রনাথ নন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত প্রথম ঘোষণা করেন বাংলা ভাষার বিজয়বাণী। মাইকেল তার অন্যতম চতুষ্পদী কবিতা ‘বঙ্গভাষা’তে বলেছেনঃ
‘হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি’
মাইকেলই আমাদের মনে উক্ত করেন ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনা, রবীন্দ্রনাথ নন। কিন্তু আজ বোঝানোর চেষ্টা চলেছে, রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা বোধের উৎস ভুমি। সেটা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এখন যে চলতি বাংলায় লিখি ও কথা বলে মনোভাব ব্যক্ত করি, তার জনক রবীন্দ্রনাথ নন। মাইকেল মধুসুদন প্রথম তার লেখা নাটকে এর প্রচলন করে যান। কিন্তু জানি না, কেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে দেয়া হয় এর জন্য কৃতিত্ব। মধুসুদন ছিলেন খুবই খোলা মনের মানুষ; কিন্তু তাই বলে তিনি চাননি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসরণ। তিনি তাই লিখেছেন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ নামে নাটক। মধুসূদনের মনে ছিল না কোনো মুসলিম-বিদ্বেষ। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো’র মতো প্রহসন লেখা। অথচ মাইকেলকে আমরা বলতে চাচ্ছি না আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস। ঘটাচ্ছি ইতিহাসের চরম বিকৃতি। যে মাইকেল আধুনিক বাংলা ভাষার ভিত গড়লেন, সাহিত্যে আনলেন নব যুগের চিন্তা-চেতনা, তাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে চলেছে রবীন্দ্র পুজা। আর এটাতে অংশ নিচ্ছেন আমাদের দেশের অনেক নামিদামি অধ্যাপক। যারা ধাঁধা লাগাচ্ছেন অনেকের চোখে।
রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় বাংলাদেশের কোনো রাজা অথবা সুলতানকে নিয়ে গৌরব চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ গৌরব গাথা রচনা করেছেন শিবাজীর। গৌরব গাথা রচনা করেছেন শাজাহানের। আমাদের দেশে বহু অধ্যাপকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ হলেন প্রগতির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছেন বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়ার। তার কাছে আদর্শ হিসেবে মনে হয়েছে তপবনের জীবন। এটা আর যাই হোক এগিয়ে থাকা মনের পরিচয়বহ নয়। রবীন্দ্রনাথ গৌরব করেছেন আর্য সভ্যতার, তার চিন্তায় ঠাঁই পেতে চায়নি অনার্য সভ্যতা। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষ কতটা ‘আর্য’ সেটা নিয়ে তোলা যেতে পারে নৃতাত্ত্বিক প্রশ্ন। বাংলা ভাষাকে স্হান দেয়া হয় আর্য বিভাগে। কিন্তু এর অনেক চরিত্রই অন্য আর্য ভাষার মতো নয়। যেমন-বাংলা ভাষায় ক্রিয়া পদ ছাড়াই বাক্য হয়, কিন্তু খাঁটি আর্য ভাষায় হয় না। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এদিক থেকে দ্রাবিড় ভাষাগুলোর সঙ্গেই মেলে। রবীন্দ্রনাথকে চিত্রিত করা হয় জাতীয়তাবাদী হিসেবে। কিন্তু এক সময় রবীন্দ্রনাথ এদশে সমালোচিত হয়েছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্হী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত গীতাঞ্জলি’র একটি কবিতায় স্বাগত করে বলেছেন মহাভারতের সাগর তীরে এদেশের মানুষের সঙ্গে একত্রিত হতে। ইংরেজ শাসনকে তিনি চেয়েছেন টিকিয়ে রাখতেই। রবীন্দ্রনাথ এদেশে যেসব তরুণ চান শক্তি প্রয়োগ করে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করতে, তাদের সমালোচনা করে লেখেন ‘চার অধ্যায়’ নামক উপন্যাস।
শরৎচন্দ্র লেখেন ‘পথের দাবি’ (১৯২৬)। শরৎচন্দ্র ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে। ব্রিটিশ সরকার ‘পথের দাবি’ উপন্যাসকে বেআইনি করে বাজেয়াপ্ত করে। অনেকে চান রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা না করে তার কাছের মানুষের কাছে মন্তব্য করেন, শরৎচন্দ্রের উচিত হয়নি ‘পথের দাবি’ লেখা। এমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ। বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে পড়ে সেভাবে বোঝেনি। তারা বরং শরৎচন্দ্রকে পড়েছে অনেক মনোযোগ দিয়ে। শরৎচন্দ্রকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডিলিট উপাধি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন ঢাকা বিশ্বাবদ্যলয়ে বাংলা বিভাগ থেকে উঠতে দেখা যায় বিশেষ বিরোধিতা। যারা এর বিরোধিতা করেন, তারা অধিকাংশই ছিলেন গোঁড়া হিন্দু আর রবীন্দ্রভক্ত।
এই ইতিহাস আমরা অনেকেই অবগত নই। বাংলাভাষী মুসলমান আর হিন্দুর মানসিক বিবর্তন একইভাবে হয়নি। হিন্দু সমাজে যখন জন্মেছে রাজা রামমোহন রায়, মুসলমান সমাজে তখন জন্মেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। রামমোহন ছিলেন মুর্তিপুজার বিরোধী। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। রামমোহনের মুত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে মন্হর বেগে চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথের দাদু মশায় প্রিস দ্বারকানাথ ঠাকুরের বরাদ্দকৃত টাকায়। পরে ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতৃত্ব দেন ব্রাহ্ম সমাজের একটা অংশকে। ব্রাহ্ম সমাজের এই অংশ রামমোহনের চিন্তা-চেতনা থেকে বেশকিছুটা ভিন্ন হয়ে পড়ে। এর ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা-চেতনা। যার প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার ওপর।
বাংলাদেশের মানুষ কি এই ভাবপ্রবাহের অংশ? প্রশ্নটা দেখা দেয় সঙ্গত কারণেই। আমরা বলেছি, হিন্দু সমাজে যখন জন্মেছেন রামমোহন, তখন মুসলমান সমাজে জন্মেছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। ইসলামী পরিভাষায় ‘ফরজ’ বলতে বোঝায় অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকে। ফরজের বহুবচন ফারায়েজ। হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমান সমাজে যে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের জন্ম দেন তা চিহ্নিত হয়ে এসেছে ফারায়েজী হিসেবে। ফারায়েজীরা ছিলেন পীর পুজার বিরোধী, দরবেশবাদের বিরোধী। তারা মনে করতেন লা-শরিক আল্লাহ। তারা মনে করতেন জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো ফরজ। অত্যাচারের কাছে মাথা নত করা অন্যায়। ফারায়েজীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে। তারা প্রতিরোধ গড়েন অত্যাচারী নীল কুঠি সাহেবেদের বিরুদ্ধেও। ফারায়েজীরা প্রথম সাহস করেন নীল কুঠিতে আগুন ধরাতে। ফারায়েজী আন্দোলন বিশেষ জোরালো রুপ পায় হাজী শরীয়তুল্লাহর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ মোহসীন ওরফে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে। বিলাতে কল-কারখানার অর্থনীতি গড়ে উঠতে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। বিলাত থেকে তৈরি সস্তা কাপড় এসে বিক্রি হতে থাকে আমাদের দেশে। যার ফলে দুর্দিন নেমে আসে আমাদের তন্তুবায়দের জীবনে। মুসলমান তন্তুবায়রা যোগ দেন দুদু মিয়ার সঙ্গে। দেশ স্বাধীন থাকলে হয়তো করারোপ করে বিদেশি বস্ত্র আসার পথ বন্ধ করা যেত। কিন্তু দেশ শাসন করছিল ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ফারায়েজী নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ধুমায়িত হয়ে ওঠে। রামমোহন ব্রিটিশবিরোধী ছিলেন না। তিনি চান ইংরেজদের সহযোগিতা করতে। হিন্দুদের উৎসাহিত করেন ইংরেজি শিখতে, কোম্পানির চাকরি পেতে। হিন্দু সমাজ আর মুসলমান মানসে এসে যায় বড় রকমেরই বিভক্তি। ১৯৭১-এর কথা আমার মনে পড়ে, মধ্য বাংলাদেশ থেকে দলে দলে বাংলাভাষী মুসলমান তরুণ যোগ দিতে আসে মুক্তি ফৌজে। এরা হলেন তাদেরই বংশধর যারা একদিন অংশ নিয়েছিলেন ফারায়েজী আন্দোলনে।
অনেক কথা এখন বলা হয় যা ইতিহাসসম্মত নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত অনেকের প্রিয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই যে আধুনিক বাংলা গানের জনক, এমন দাবি সঙ্গত নয়। বাংলা গানে নতুন ধারার প্রথম সৃজক হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। আমরা অনেকে চেয়েছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ও সুর দেয়া গান ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা’কে জাতীয় সঙ্গীত করতে। কিন্তু ভারত সরকারের চাপে পড়ে তাজউদ্দিন সরকার গ্রহণ করে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি। গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ও সুর দেন ১৯০৫ সালের কাছাকাছি, লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের বিপক্ষে আন্দোলনকে তীব্র করার লক্ষ্যে। বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে আন্দোলন খুব তীব্র হয়েছিল, যার ফলে কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়ে যায়। বঙ্গ ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা মুজাফফর আহমদ তার স্মৃতিকথামুলক গ্রন্হ ‘আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট’-এ এক জায়গায় বলেছেন-পুর্ব বঙ্গে বড় বড় হিন্দু জমিদার বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। জমিদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, মুসলিম কৃষক প্রজাপ্রধান পুর্ব বঙ্গে না জমিদারি প্রথা বিলোপ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ একরকম ভয়ে ভীত ছিলেন। আর তাই রচনা করেন ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি, যা এখন বিশেষ কারণে হতে পেরেছে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ ভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়ার পর রাজা পঞ্চম জর্জকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ও সুর দেন তার ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ গানটি, যা এখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত অবশ্য একটি নয়, দুটি। আরেকটি জাতীয় সঙ্গীত হলো বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘বন্দে মাতরম’। এই গানটি এখন যে সুরে গাওয়া হয় তাও রবীন্দ্রনাথেরই দেয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এবং রবীন্দ্রনাথের সুরারোপিত গানটি গাওয়া হতো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। গীত হতো হিন্দু মেলা আনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথকে তাই এদিক থেকেও আজকের বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা ইতিহাসসম্মত নয়। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে উৎকল ও বঙ্গের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর কথা। সাধারণভাবে দাক্ষিণাত্যের সবাইকে বলা হয়েছে দ্রাবিড় হিসেবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গানে আসামের উল্লেখ নেই। ইচ্ছা করেই রবীন্দ্রনাথ মনে হয় আসামের উল্লেখ করতে চাননি। কারণ কার্জন পুর্ব বাংলা এবং তখনকার আসামকে যুক্ত করে গড়েছিলেন একটি প্রদেশ, যার প্রাদেশিক রাজধানী হয়েছিল ঢাকা। আর মুল বন্দর হয়েছিল চট্টগ্রামে। মুসলিমপ্রধান পুর্ব বঙ্গের এবং উত্তর বঙ্গের মানুষ সমর্থন করেছিল বঙ্গ ভঙ্গকে। আমরা এখন ইতিহাসের অনেক ঘটনাকেই ভুলে যেতে চাচ্ছি। আর তাই অনেক সহজেই বলতে পারছি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস।
আমি নওগাঁর পতিসরে একাধিকবার গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের কাচারি বাড়ির ঠিক পেছনে আছে একটি বড় দীঘি। সাধারণত জমিদার বাড়ির সঙ্গে যেরকম দীঘি সংলগ্ন থাকতে দেখা যায়। একজন প্রাচীন ব্যক্তির মুখে শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম, ওই দীঘিতে ছিল না কোনো মুসলমানের স্নান করার অধিকার। ঠাকুর পরিবার এদিক থেকে যে উদার ছিল তা মোটেও নয়। পতিসরে রবীন্দ্রনাথের মুসলমান প্রজাদের খাজনা দিতে হতো পৃথকভাবে। ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করেই জেনেছি এই ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে এক সময় কোনো মুসলমান ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চাঁদা চেয়েছিলেন হায়দরাবাদের নিজামের কাছেও। নিজাম তাকে চাঁদা দেন এক লাখ টাকা। এক লাখ টাকা সে সময় ছিল অনেক। রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পারেননি নিজাম এতটা চাঁদা দেবেন। নিজামের চাঁদার সুত্র ধরেই সামান্য কিছু মুসলিম ছাত্র সুযোগ পায় বিশ্বভারতীতে লেখাপড়া শেখার। সাহিত্যিক মুজতবা আলী হলেন যাদের মধ্যে একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। হিন্দুরা চাননি ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হোক। এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আসলে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।
শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথও চাননি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হোক। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতী নামে তার বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর যাত্রা শুরু হয় প্রায় একই সঙ্গে। বিশ্বভারতী মুসলিম ছাত্রদের আকর্ষণ করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলেই পুর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব হতে পারে, যা মুসলিম জাগরণে পালন করে বিশেষ ভুমিকা। অর্থাৎ ইতিহাসের নিরিখে দেখলে বলতে হয়-রবীন্দ্রনাথ নয়, যারা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপনের উদ্যোগ নেন, তারাই আনতে সাহায্য করেন পুর্ব বঙ্গের মুসলিম জাগরণ। যা আজকের বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তিভুমি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ভর করে পাকিস্তান আমলে সৃষ্টি হতে পারে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। বিশ্বভারতী অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভাষা নিয়ে এ ধরনের কোনো আন্দোলনে ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হিন্দিকেই তারা মেনে নিতে চেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। আসলে রবীন্দ্রনাথও তার বাংলা ভাষা পরিচয় নামক বইতে এক জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন-‘হিন্দি হওয়া উচিত নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা।’
তাই আজ যারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথ হলেন আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস, তাদের এই দাবি ইতিহাসের ধোপে টেকে বলে মনে হয় না। আজ বাংলা ভাষার ইতিহাসকে এমনভাবে পড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার স্রষ্টা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সাহিত্যিকদের কাব্য সাধনায় সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি, যেভাবে করেছিলেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। মুসলমান কবি মোহাম্মদ কাজেম ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৪-১৯৫১) মধুসুদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন ‘মহাশ্মশান’ কাব্য (১৯০৪); যার বিষয়বস্তু হলো পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ মারাঠা শক্তির জয়গান করেছেন, কিন্তু মুসলমান কবিরা মারাঠাদের ভেবেছে পরাস্ব অপহরণকারী হিসেবে।
বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনা বিশেষভাবে শুরু হয় ইংরেজ আমলে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) লিখেছেন চমৎকার বাংলা গদ্য। মীর বাংলা গদ্য লেখা শেখেন সাপ্তাহিক গ্রাম বার্তা পত্রিকার সম্পাদক কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে। যে কাঙ্গাল হরিনাথকে রবীন্দ্রনাথের পিতা খুন করার জন্য গুন্ডা লেলিয়ে দেন। কাঙ্গাল হরিনাথের অপরাধ ছিল, তিনি ঠাকুর পরিবারকে সমালোচনা করেন অত্যাচারী জমিদার হিসেবে। এটাও একটা বিশেষ ইতিহাস। বাংলার মুসলমান তাদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে যে পরিমাণ ঋণী, অন্য কারো কাছে তা নয়। কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথকে নিয়ে আমাদের পত্র-পত্রিকায় তেমন কোনো আলোচনা হতে দেখা যায় না। ‘গ্রামবার্তা’ পত্রিকা প্রকাশিত হতো কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে, যা হয়ে উঠেছিল এদেশে নিপীড়িত কৃষক প্রজার বিশেষ মুখপাত্র। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার শিলাইদহে থেকেছেন অনেক দিন। যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, তাকে বলা হয় কুঠিবাড়ি। এটা নির্মাণ করেছিলেন এক নীল কুঠি সাহেব। যার নাম ছিল শেলি। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই কুঠি বাড়িটি ক্রয় করেন। শিলাইদহের জমিদারি রবীন্দ্রনাথের ছিল না। এই জমিদারি পড়েছিল খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের।