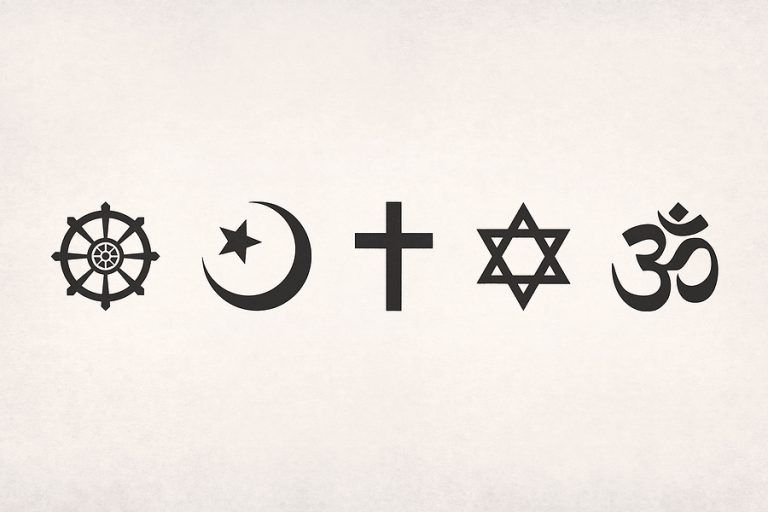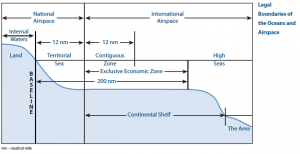ক’দিন ধরে পত্রপত্রিকায় চট্টগ্রাম বিভাগের বৌদ্ধ-মুসলিম সঙ্ঘাতের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এই সঙ্ঘাত যত না ঘটছে ধর্মীয় কারণে, তার চেয়ে অধিক ঘটছে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম জড়িয়ে পড়ছে রাজনীতির সাথে, তাই এ নিয়ে কিছু সাধারণ আলোচনা হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক।
ধর্মচেতনার দিক থেকে আদিতে বৌদ্ধ ধর্ম ছিল অন্যান্য ধর্মের থেকে যথেষ্ট আলাদা। একে ঠিক একটি ধর্মচেতনা বলা যায় না। ধর্মের ভিত্তি হলো ঈশ্বর বা স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চাননি কিছু বলতে। তিনি চেয়েছেন মানুষের দুঃখ নিবৃত্ত করতে। চেয়েছেন মানুষের জীবনে আনতে প্রশান্তি, যাকে আরেক কথায় বলা হয় নির্বাণ। মানুষের দুঃখের একটা কারণ হলো বাসনা। মানুষ অনেক কিছু পেতে চায়, কিন্তু তা সে পেতে পারে না। আর যেহেতু সে পেতে পারে না, তাই হয় অসুখী। সুখী হতে হলে তাই বাসনাকে কমাতে হবে। তাহলে লাঘব হতে পারবে আমাদের বেদনা। এ হলো বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাধারণ অনুজ্ঞা।
দুঃখের আর একটি বিশেষ কারণ হলো হিংস্রতা। সুখী হতে হলে তাই করতে হবে হিংস্রতা পরিহার। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার একটি মূলমন্ত্র তাই অহিংসা বা হিংস্রতা থেকে নিবৃত্তি। গৌতম নিষিদ্ধ করেছেন প্রাণী হত্যা। কারণ প্রাণী হত্যার মাধ্যমে প্রশ্রয় পায় মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তি। বৌদ্ধ মতে, উদ্ভিদের জীবন আছে কিন্তু আত্মা নেই। তাই তাদের আহার করা চলে। তাতে মানুষের হিংস্রতার প্রসার ঘটতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মে দুগ্ধকে ধরা হয় নিরামিষ। কারণ দুগ্ধপানে প্রাণী হত্যা হয় না।
আধুনিক বিজ্ঞান বলে, প্রাণীদের মতো উদ্ভিদের আছে বেদনাবোধ। উদ্ভিদ ভোজনকে তাই অহিংসার পরিপন্থী বলা চলে না। বৌদ্ধ ধর্মে অবশ্য অনেক দিন বিতর্ক চলেছে বৃক্ষের আত্মা আছে কি নেই, সেটা নিয়ে। কিন্তু একপর্যায়ে এসে বৌদ্ধরা মনে করেছেন, বৃক্ষের আত্মা নেই। তাই তাদের নেই মানুষের মতো সুখ-দুঃখের অনুভব। তবে বৃক্ষের মধ্যে অশরীরী আত্মারা আশ্রয় নিতে পারে। এদের বলা হয়েছে যক্ষ। ইচ্ছামতো নানা রূপ ধারণ করতে পারে যক্ষরা। যক্ষের ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে অধিকার করেছে বিশেষ স্থান। বৌদ্ধরা চেয়েছেন নানাভাবে অপযক্ষের প্রভাব এড়াতে।
বৌদ্ধ ধর্মে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী। কিন্তু শেষে বৌদ্ধরা হয়ে উঠেছেন মূর্তিপূজারী। যে গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর আছেন কি নেই, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি, তিনিই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছেন পরম ঈশ্বর। বৌদ্ধ ধর্মে ঢুকে পড়েছে স্বর্গ, নরক আর নানা দেবদেবীর ধারণা। তা গৌতম বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা থেকে হয়ে পড়েছে বিশেষভাবেই ভিন্ন। বৌদ্ধ ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, স্তূপের পূজা। প্রাচীন যুগে কোনো মানুষ মারা গেলে তার স্বজনেরা তাকে কবর দিয়ে এর ওপর গড়ত মাটির ঢিবি। আর অনেক ক্ষেত্রে স্তূপকে প্রদক্ষিণ করে মৃত আত্মার পূজা করেছে। একপর্যায়ে স্তূপের পূজা বিশেষ করে যুক্ত হয়ে পড়েছে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে।
বৌদ্ধদের স্তূপ হলো চার প্রকারÑ শরীর স্তূপ, পরিভৌগিক স্তূপ, নির্দেশিক স্তূপ ও নিবেদন স্তূপ। শরীর স্তূপ বলতে বুঝায় বুদ্ধদেব এবং তার অনুচর ও শিষ্যবর্গের দেহাবশেষ যেসব স্তূপে রক্ষিত আছে অথবা আছে বলে মনে করা হয় সেই সব স্তূপকে। পরিভৌগিক স্তূপ বলতে বুঝায় সেই সব স্তূপকে, যাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিস রক্ষিত আছে অথবা আছে বলে মনে করা হয়। নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ বলতে বুঝায় বুদ্ধদেবের জীবন-ইতিহাসের সাথে জড়িত স্থানে নির্মিত স্তূপকে। নিবেদন স্তূপ বলতে বুঝায় কেবলই পূজার জন্য নির্মিত স্তূপকে।
ইসলামে মূর্তিপূজা নেই; নেই স্তূপের পূজা। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে কতগুলো বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কাবাগৃহ হলো মুসলমানদের সর্বোচ্চ পবিত্র তীর্থস্থান। হজব্রত পালনের সময় কাবাগৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। চারবার দ্রুত ও তিনবার মন্থর বেগে। এটা হলো কতকটা বৌদ্ধদের স্তূপ প্রদক্ষিণেরই মতো। হজ করার সময় পুরুষেরা কোনো সেলাই করা জামা পরতে পারেন না। তাদের পরিধান করতে হয় দুই টুকরা সেলাই না করা বস্ত্র। এক টুকরা কাপড় ব্যবহার করতে হয় দেহের নিম্নভাগ ঢাকার জন্য। আর অপর টুকরা কাপড় দিয়ে আবৃত করতে হয় বক্ষ ও স্কন্ধ। মাথা অনাবৃত রাখতে হয়।
আগে নিয়ম ছিল হজের সময় পুরুষের মস্তক মুণ্ডন করার; কিন্তু এখন চুল খুব ছোট করে কাটলেও চলে। পুরুষের এই পোশাক মনে করিয়ে দিতে চায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (সন্ন্যাসীদের) পরিধেয় বস্ত্রের কথা। মহিলারা হজ করার সময় স্বাভাবিক জামা পরিধান করতে পারেন। কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল রাখতে হয় অনাবৃত। বোরখার মতো কোনো কিছু পরিধান করা যায় না হজের সময়। কাবাগৃহ ও তার নিকটস্থ কোনো স্থানে প্রাণী হত্যা একেবারে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ হজব্রত পালনের সাথে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মের সাথে। আর এর মধ্যে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায় অহিংসার প্রবণতা। ইসলাম মানুষকে নিরামিষভোজী হতে বলেনি; কিন্তু খাদ্য হিসেবে প্রাণী হত্যাকে সমর্থন করলেও ইসলামে তা করতে বলা হয়েছে প্রাণীদের সবচেয়ে কম কষ্ট দিয়ে। ইসলামের এই নির্দেশের মধ্যেও দেখা যায় একটা অহিংসতার প্রবণতা।
ইসলাম মানুষকে হিংস্র হতে উৎসাহ জোগায়নি। কুরআন শরিফে আছে ১১৪টি অধ্যায় বা সূরা। এর মধ্যে একটি ছাড়া সব ক’টি সূরায় শুরুর প্রারম্ভেই বলা হয়েছেÑ আল্লাহ পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। করুণা ও ক্ষমা ইসলামেরও অন্যতম দু’টি অনুজ্ঞা। খলিফা আবুবকর রা: তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেনÑ ‘ন্যায়পরায়ণ হবে। কারণ অন্যায় আচরণকারীরা শেষ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না। সাহসী হবে, মৃত্যুবরণ করবে; আত্মসমর্পণ করবে না। সদয় ব্যবহার করবে। বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী লোকের গায়ে হাত তুলবে না। ফুলগাছ নষ্ট করবে না। নষ্ট করবে না খাদ্যশস্য ও গৃহপালিত পশু। কদাচ রূঢ় ব্যবহার করবে না আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের সাথে। (Syed Ameer Ali; History of the Saracens, Chapter- ৪)। ঐতিহাসিকদের মতে, একসময় সিরিয়া অঞ্চলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র। সিরিয়াতে ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম। এখানে আশ্রমবাসী বলতে মূলত বোঝানো হয়েছে মূল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। তারাই বাস করতেন ওইসব আশ্রমে। রাজা অশোক সিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।
ইসলামে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে। জিহাদ হলো তিন প্রকার : কাজের দ্বারা (ফিল), কথার দ্বারা (কাওল) এবং অস্ত্রের দ্বারা (কতল)। ইসলামি মতে, ভালো কাজ করে মন্দ কাজ প্রতিরোধ হলো জিহাদ। উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করা জিহাদ। অর্থের দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা হলো জিহাদ। ইসলামে প্রথমে অস্ত্র ধারণ করতে বলা হয়নি। অস্ত্র ধারণ করতে বলা হয়েছে সর্ব শেষ পর্বে। কুরআন শরিফে বলা হয়েছেÑ আল্লাহ আক্রমণকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা ২; ১৯০-১৯৩)। ‘ইসলামি মৌলবাদ’ নিয়ে বেশ কিছু দিন হলো অপপ্রচার চলছে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে রক্তপাতে উৎসাহ প্রদান করে না। ইসলামের মূল শিক্ষা ক্ষমা, মৈত্রী ও ভালোবাসা; রক্তপাত নয়। আমরা এসব কথা বলছি এ জন্য যে, এখন বোঝানোর চেষ্টা চলছেÑ ইসলাম একটা জঙ্গিবাদী ধর্ম। কিন্তু ইসলামে শক্তি প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে জুলুম বন্ধ করার জন্য। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামে অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)।
চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঠিক কী হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানি না। কিন্তু মনে হয়, এ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা হবে যে, ‘মুসলমানেরা চাচ্ছেন বৌদ্ধধর্মীদের বিনাশ করতে। কারণ মুসলমানেরা হলেন নীতিগতভাবেই জঙ্গিবাদী। তারা চান অস্ত্রের জোরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিনাশ করতে।’ কিন্তু এটা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর ধারণা নয়। প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। এই রাজারা রাজত্ব করেছেন বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে এবং বর্তমান বিহারের মগধ অঞ্চলে। তারা ছিলেন বঙ্গ ও মগধের শাসনকর্তা। পাল রাজত্বের পর বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসেন সেন বংশের রাজারা। তারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের ওপর বেড়েছিল হিন্দুদের অত্যাচার। সেন রাজাদের পতন ঘটে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাতে। হিন্দু রাজাদের এই পরাজয়কে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা জানান বিশেষভাবেই স্বাগত। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি মুসলমানগণ হিন্দু অত্যাচার থেকে রক্ষা করার বাহিনী।
বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধকে একপর্যায়ে ধর্মঠাকুর হিসেবে পূজা করা শুরু হয়। ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কে লিখিত একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটির নাম ‘ধর্মপূজা বিধান’। এর বয়সকাল নির্ধারণ করা যায়নি। এই পুঁথিতে ‘নিরঞ্জনের রূস্মা’ নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সাথে কী রকম দুর্ব্যবহার করতেন তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই কবিতায়। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ভয়ে ধর্মঠাকুরের পূজারীরা ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠেছিল। বিচলিত ভক্তরা ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তাদের প্রার্থনা শুনে বৈকুণ্ঠে (স্বর্গে) ধর্মঠাকুরের আসন টলে ওঠে। এই কবিতায় লেখা হয়েছে,
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
বিষ্ণু হইল পয়গম্বর ব্রহ্মা হৈল পাকাম্বর
আদম্ভ হইয়া শূলপাণি।
এইরূপে গণেশ হলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি ও পদ্মাবতী হলেন বিবি নূর। এভাবে দেবতাগণ মুসলমানের রূপ ধারণ করে জাজপুরে প্রবেশ করে ভাঙল হিন্দুদের মন্দির। সৃষ্টি করল মহা-অনর্থ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, দলে দলে বৌদ্ধরা মুসলমানদের সাথে যোগ দেন এবং গ্রহণ করেন ইসলাম (শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার; বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)। বাংলাদেশে তাই গায়ের জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়Ñ এই দাবিকে ঐতিহাসিক বলে সমর্থন দেয়া যায় না। এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে দলে দলে বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে গ্রহণ করতে থাকেন ইসলাম। এই অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের ছিল নিবিড় বাণিজ্য সম্পর্ক। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলাম প্রচারের একটা প্রভাব সম্ভবত এসে পড়েছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ওপর।
দক্ষিণ ভারতে জাফর শরীফ ‘কানুন-ই-ইসলাম’ নামে একটি বই লেখেন। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন G. A. Herklot। বইটির নাম দেন Islam in India। পরে এই অনুবাদকে ১৯২১ সালে ঢেলে সাজান ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ ড. ক্রুক। এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ক্রুক বলেনÑ বাংলাদেশে হিন্দুরা মুসলমান হননি, হয়েছেন বৌদ্ধরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বড়–য়া ‘মগ’রা দাবি করছেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে গিয়েছিলেন বিহারের মগধ অঞ্চল থেকে।
বড়–য়া মগদের দাবি, তাদের মগ বলা হয়, কারণ তাদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন মগধ থেকে। মগধ থেকেই হতে পেরেছে মগ নামের উদ্ভব। কিন্তু চাকমা ও বড়–য়া মগরা যে বৌদ্ধ ধর্মকে এখন অনুসরণ করছেন, তা হলো থেরাবাদী বৌদ্ধ ধর্ম, যা এসেছে মিয়ানমার থেকে। ‘মগ’ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভারত কোষের সপ্তম খণ্ডে বলা হয়েছেÑ মগ বলতে বোঝায় আরাকানবাসী এবং ১৮ শ’ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত আরাকানি উদ্বাস্তুদের। সম্ভবত বর্মি উপাধি ‘মোভ’ থেকে মগ নামের উদ্ভব হয়েছে। ভারত কোষে আরো বলা হয়েছে, আরাকানি মগরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে একত্রে অথবা পৃথকভাবে শুরু করে জলদস্যুতা। এদের এই জলদস্যুতার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের ভয়ংকর ক্ষতি হয়েছিল।
মগ জলদস্যুরা বাংলাদেশ থেকে শত শত মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত দাসরূপে। বাংলা ভাষায় তাই ‘মগের মুল্লুক’ বলতে বুঝায় ভীতিপ্রদ অরাজক রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিকে। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ফলে ঘটা সম্ভব হয় মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের অবসান। বাংলাদেশের রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করার একটি কারণ ছিল, সুবে বাংলাকে মগ জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করা। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরাকান ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় ব্রহ্মরাজের ভয়ে ভীত হয়ে বহু আরাকানবাসী সাবেক চট্টগ্রাম জেলার প্রান্তভাগে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মগদের সন্তানসন্ততিকে এখন আমরা বলি প্রকৃত মগ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদের বলা হয় প্রকৃত মগ, তারা বাস করেন প্রধানত কক্সবাজার জেলায়। এরা হলেন বড়–য়া মগদের থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। বড়–য়া মগদের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। তারা কথা বলেন চট্টগ্রামের বাংলায়। পক্ষান্তরে মগরা এখনো তাদের নিজ ভাষায় কথা বলেন নিজেদের মধ্যে। তারা তাদের এই ভাষা লেখার জন্য ব্যবহার করেন বর্মি (ম্রনমা) অক্ষর। মগদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক লেখাপড়া শেখে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে।
মগ ও বড়–য়া মগদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে অবগত নই। উত্তম কুমার বড়–য়া নামক একজন বৌদ্ধ বড়–য়া মগ কুরআন শরিফের অবমাননা করেছে। প্রকৃত মগরা এর সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নন। উত্তম কুমার বড়–য়ার অপরাধে সব মগকে অভিযুক্ত করা খুবই বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তির ফলে ঘটতে পেরেছে প্রকৃত মগদের ওপর কক্সবাজার জেলায় সাম্প্রতিক হামলা। অনেক কিছুই ঘটছে, যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যেমনÑ উত্তম কুমার বড়–য়া ফেসবুকে কুরআন শরিফ অবমাননার ছবি প্রকাশ করার আধা ঘণ্টা না যেতেই শুরু হলো রামুতে হাঙ্গামা। মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে এত লোক একত্র হয়ে লুটপাট চালাতে পারে না। তা ছাড়া, লুটপাটের সময় প্রশাসন থাকল উদাসীন হয়ে। তাই মনে হচ্ছে, যা কিছু ঘটছে তার মূলে আছে একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ সরকার প্রচার করতে ব্যস্তÑ এটা ইসলামি মৌলবাদীদের চক্রান্তের ফল। কিন্তু ক্ষমতা এখন কোনো মৌলবাদী সরকারের হাতে নেই। ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ সরকার। তারা কেন যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করল না? বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন শক্তিধর মন্ত্রী হলেন দিলীপ বড়–য়া। যত দূর জানি, দিলীপ বড়–য়া হলেন বড়–য়া মগ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারছে জনমনে।
বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে খুব সরব ছিল এবং এখনো আরো সরব হয়ে উঠেছে ভারতের প্রচারমাধ্যম। এটা হওয়া তাদের দিক থেকে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা কি খুবই ভালো? ১৯৫০-এর দশকে ভারতের বিখ্যাত নিম্নবর্ণের হিন্দু নেতা, ভারতের সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা ড. আম্বেদকর ভারতের সব নিম্নবর্ণের হিন্দুকে বলেছিলেন বৌদ্ধ হতে। ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আম্বেদকরের উপদেশ শুনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এর ফলে হিন্দুদের কাছে তারা উন্নত ব্যবহার পেতে পারছেন না। তারা আছেন আগের মতোই ভিন্ন ও অস্পৃশ্য হয়ে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশে বৌদ্ধরা কি এভাবে অবহেলিত?
পত্রিকা পড়ে জানলাম, বাংলাদেশের কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু দাবি তুলেছেন, বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর জন্য। কিন্তু এ রকম দাবি ওঠানো কি খুবই সঙ্গত হচ্ছে? জাতিসঙ্ঘের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী নেই। অন্য দেশের সেনাবাহিনীর সৈন্যরা চুক্তিভিত্তিকভাবে কাজ করেন জাতিসঙ্ঘের রক্ষীবাহিনীতে। এতে যারা অধিক সংখ্যায় কাজ করেন, তারা হলেন ভারত ও বাংলাদেশের সৈন্য। বাংলাদেশে যদি জাতিসঙ্ঘের হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা আসতে চান, তবে চীন তার আপন স্বার্থেই করবে এর বিরোধিতা।
পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দুর্বল রাষ্ট্র হলেও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ কখনোই চাইতে পারেন না এ দেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যদি বিদেশী হস্তক্ষেপ কামনা করতে থাকেন, তবে তাদের সাথে বাড়তে থাকবে এ দেশের বৃহত্তর জনসমাজের অর্থাৎ বাংলাভাষী মুসলমানদের মনোমালিন্য। সৃষ্টি হবে আরো জটিল ও সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতির। বাংলাদেশে মুসলমান-বৌদ্ধ সঙ্ঘাত যদি দু’টি সভ্যতার সঙ্ঘাতে রূপ নিতে চায়, তবে পরিস্থিতি হয়ে উঠবে আরো ভিন্ন। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক মুসলিম দেশ সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে পারে বাংলাদেশের দিকে। তখন সমস্যাটি হয়ে উঠতে চাইবে আন্তর্জাতিক।
লেখক : প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট