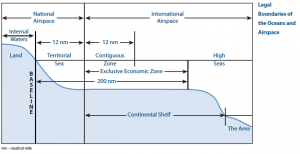সাঁওতালদের নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এসব আলোচনা যথেষ্ট ইতিহাসভিত্তিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সাঁওতালদের বলা হচ্ছে, এ দেশের অন্যতম আদিবাসী (Aborigine)। কিন্তু সাঁতালরা এ দেশের ভূমিপুত্র নয়। তাদের বলতে হয় আগন্তুক উপজাতি (Tribe)। সাঁওতালদের লোককথায় বলে, তারা এসেছে, হিহিড়ি পিপিড়ি দ্বীপ থেকে। কিন্তু এই হিহিড়ি পিপিড়ি দ্বীপ ঠিক কোথায়, সেটা এখনো নির্ণয় করা যায়নি। সাঁওতালদের নৃতত্ত্বের বইয়ে সাধারণত স্থাপন করা হয় প্রোটো-অস্ট্রালয়েড মানবধারায়। প্রটো-অস্টোলয়েড নামটা দেন ড. বিরোজা শঙ্কর গুহ, ১৯৩১ সালের আদমশুমারির সময়। তিনি এ সময় ছিলেন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। তিনি নামটা চয়ন করেন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, হো, কোল, ভিল প্রভৃতি উপজাতিকে বর্ণনা করার জন্য। প্রটো-অস্টোলয়েড কথাটির বাংলা আমরা করতে পারি প্রায়-অস্ট্রালয়েড। এদের এই নাম দেয়া হয়েছে, কেননা এদের চেহারার সৌসাদৃশ্য আছে অস্ট্রেলিয়ার আদিম কালো মানুষদের সঙ্গে। অবশ্য পার্থক্যও আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রটো-অস্ট্রোলয়েড মানবধারার মানুষদের চেয়ে দৌহিক উচ্চতায় হয় বেশি এবং ভুরুর হাড় হয় অনেক উন্নত। এদের কপালের মধ্যভাগ প্রটো-অস্ট্রোলয়েডদের তুলনায় বেশ কিছুটা নিচু। প্রটো-অস্ট্রোলয়েডদের গায়ের রঙ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মতোই কালো। মাথার চুল মোটা ও ঘন। তবে মসৃণ। নাকের অগ্রভাগ মোটা ও মাংসল। কিন্তু চ্যাপটা নয়। মাথার আকৃতি লম্বা।
নৃতত্ত্বে মানবধারা বিভাগের সময় মাথার আকৃতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়। লম্বা মাথা বলতে বোঝায় এমন মাথা, যার প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৭৫ বা তার কম। মাঝারি মাথা বলতে বোঝায়, যাদের প্রস্থ হলো দৈর্ঘ্যরে শতকরা ৭৫ ভাগ থেকে ৮০ ভাগের মধ্যে। আর গোল মাথা বলতে বোঝায় সেই সব মাথাকে, যাদের প্রস্থ দৈর্ঘ্যরে শতকরা ৮০ ভাগ অথবা তার বেশি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের মাথা মধ্যমাকৃতির অথবা গোল। সাঁওতালদের মতো লম্বাকৃতি নয়। তাই সাঁওতালদের মতো মানুষের থেকে বাংলাদেশের মানবসমষ্টির উদ্ভব হতে পেরেছে, এ রকম সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে না। যেমন আগে অনেকে করতেন।
১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে বর্ধমান জেলার পাণ্ডু রাজার ঢিবি এবং বিরভুম জেলার মহিষাদল নামক জায়গায় উৎখনন চালানো হয়। এর ফলে তাম্র-প্রস্তর যুগের এক উন্নত সভ্যতার আবিষ্কার হতে পেরেছে। এখানে পাথরের অস্ত্রের সাথে তামার জিনিস পাওয়া গেছে। তামার তৈরি জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেছে মাছ ধরার বড়শি। যার সাহায্যে এই জায়গার এই সময়ের মানুষ মাছ ধরে আহার সম্পন্ন করত। মহিষাদলে একটা পোড়ামাটির পাত্রের মধ্যে কিছু কয়লা হয়ে যাওয়া ধান পাওয়া গেছে। রেডিও অ্যাকটিভ কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে যার বয়স নির্ণিত হয়েছে ১৩৮০ থেকে ৮৫৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। যার থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই সময় মানুষ ধানচাষ করে তা থেকে চাল উৎপাদন করে আহার করত। অর্থাৎ এদের জীবন ছিল আমাদেরই মতো মাছ-ভাতনির্ভর। মানুষ এই সময় এখানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করত। শবদেহ শায়িত করত পূর্ব-পশ্চিমে। এসব মানুষের মাথার খুলি হলো মধ্যমাকৃতির। সাঁওতালদের মতো লম্বাকৃতির নয়। এদের মাথার আকৃতির সাথে সাদৃশ্য আছে বাংলাদেশের বিরাটসংখ্যক জনসমষ্টির মাথার। তাই ধারণা করা যায়, আমরা অনেকে বহন করছি এসব মানুষের জীবনধারাকে। এসব কবরে পাওয়া গেছে বৈশিষ্ট্যময় মৃৎপাত্র। যার অনুরূপ মৃৎপাত্র এখনো কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের পত্রপত্রিকা পড়ে মনে হচ্ছে, সাঁওতালরা হলো এ দেশের আদিবাসী। আর আমরা হলাম পরদেশী। যেটা সত্য নয়।
ইংরেজি ভাষায় ট্রাইব শব্দটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ট্রাইব কথাটার বাংলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হয়েছিল উপজাতি। বাংলায় উপজাতি বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টি, যারা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। যারা বাস করে সভ্যমানুষের কাছাকাছি। কিন্তু যাদের সভ্যতা পড়ে আছে প্রস্তরযুগের পর্যায়ে। যারা বাস করে দুর্গম পাহাড়ি ও আরণ্যক অঞ্চলে। যারা লাঙ্গল দিয়ে কৃষিকাজ করতে জানে না। যারা মাটিতে কাঠের খুঁটা দিয়ে গর্ত করে বীজ বপন করে চাষাবাদ করে। যাকে বলা হয় জুম অথবা ধাইয়া। এ ছাড়া এই চাষপদ্ধতির অন্য নামও আছে। তবে এসব মানুষ চাষাবাদের চেয়ে বন্য ফলমূল আহরণ ও পশু শিকার করে খেতেই বিশেষ অভ্যস্ত। এদের প্রত্যেকের একটি করে ভাষা আছে। কিন্তু ভাষাটা লিখিত নয়। সাঁওতালদের ধরা হয়েছে একটা উপজাতি। কেননা, এরা সবাই দেখতে একই রকম, একই ভাষায় কথা বলে এবং বাস করে একত্রে। এ ছাড়া এদের ধর্মবিশ্বাসও এক। অর্থাৎ উপজাতি বলতে এসেছে মানবধারা, ভাষা ও ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গ।
উপজাতি ও জাতির মধ্যে পার্থক্য হলো, জাতির জনসমষ্টি হলো অনেক বেশি। ভাষা এক। কিন্তু একটি জনসমষ্টির মধ্যে থাকা সম্ভব একাধিক মানবধারার মানুষ। যেমন আছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে। জাতি আর উপজাতিকে এক করে দেখা যায় না। একটি উপজাতি এসে বসবাস আরম্ভ করতে পারে একটি জাতির মধ্যে। যেমন সাঁওতালরা করছে আমাদের মধ্যে। সাঁওতালরা বাস করছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। এদের নীলকর সাহেবরা নিয়ে আসে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে মালদহের পূর্বাঞ্চলে নীলচাষ করার জন্য। সেখান থেকে এরা ছড়িয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়।
বিখ্যাত ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ গ্রিয়ার্সন লিখেছেন সাঁওতালদের মালদহের পূর্বাঞ্চলে নিয়ে আসবার কথা (G. A. Grierson: Linguistic Survey of India, Vol 4, 1906. Page 30-33pp)| গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঠিক কী হয়েছে আমরা তা জানি না। যেহেতু বিষয়টি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে বলে মনে করছি না। তবে সাঁওতালদের আমাদের পত্রপত্রিকায় যে রকম নিরীহ বলে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, সাঁওতালদের ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ১৮৫৫ সালে ৩০ জুন ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। এতে অংশ নেয় প্রায় ৫০ হাজার সাঁওতাল। এই সাঁওতালরা যে কেবল হিন্দু সুদখোর মহাজনদেরই খুন করেছিল, তা নয়। খুন করেছিল বহু বাংলাভাষী নিরপরাধ হিন্দুকে। করেছিল তাদের বাড়িঘর লুট। বিদ্রোহ থামানোর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনকে জারি করতে হয়েছিল সামরিক আইন। সৈন্যবাহিনীর গুলিতে মারা গিয়েছিল প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল। সেটা অনেক দিন আগের কথা।
তখন সবে পাকিস্তান হয়েছে। কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের নির্দেশে সাঁওতালরা করে নাচোল থানা অধিকার। তাদের ল্য ছিল এই অঞ্চলে একটা মুক্ত রাজ্য স্থাপন। সাঁওতালরা নাচোল থানা দখল করতে গিয়ে থানার দারোগা ও তিনজন কনস্টেবলকে মেরে ফেলে। এটা ঘটেছিল ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি। ঘটনাটিকে কোনোভাবেই একটা নিরীহ অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতের বিহারে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতালরা ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির আন্দোলনের অনুকরণে ঘটায় অভ্যুত্থান। যেটা দমন করতে ভারতীয় সাধারণ পুলিশ এবং বিশেষ মিলিশিয়াকে চালাতে হয় গুলি। সাঁওতাল, পুলিশ ও মিলিশিয়া মিলে এ সময় মারা যায় প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তি। এর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না সাঁওতালদের নিরীহ সরল চরিত্রকে।
বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় (১৯ নভেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়) একটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধটির নাম নিভৃত সাঁওতালপল্লীতে বিষাদের কালো ছায়া। প্রবন্ধটি লিখেছেন লে. জে. মাহবুবুর রহমান (অব.)। শুনেছি তিনি নাকি বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ উপদেষ্টা। তাই বাড়তি কৌতূহল নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম প্রবন্ধটি। কিন্তু খুব বিস্মিত হলাম, আমাদের খ্যাতনামা লে. জে. প্রবন্ধটিতে বলছেন, সাঁওতালদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে সংবিধানে। দিতে হবে সাঁওতালি ভাষার রাষ্ট্রিক মর্যাদা। অথচ বিএনপির নেতা জিয়াউর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা। তিনি দিতে চাননি কোনো ক্ষুদ্র নৃ-জাতিক জনসমষ্টিকে সংবিধানে পৃথকভাবে স্বীকৃতি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অনুসারে এ দেশের সাঁওতালদের বাস করতে হবে বৃহত্তর জনসমষ্টির সাথে বাংলাদেশী সাঁওতাল হয়ে; পৃথক সাঁওতাল জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গি নিয়ে নয়। জেনারেল মহোদয়ের চিন্তাচেতনা বিএনপির মূল দর্শনের সঙ্গেই যেন হতে পারছেন সাংঘর্ষিক। তিনি সম্ভবত জানেন না যে, ২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর বিহার থেকে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে পৃথক করে গঠন করা হয়েছে নতুন প্রদেশ ঝাড়খণ্ড। ভারতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সাঁওতাল বাস করে বর্তমান ঝাড়খণ্ড প্রদেশে। ঝড়খণ্ড প্রদেশে সরকারি ভাষা করা হয়েছে দেবনাগরী অরে লেখা বিশুদ্ধ হিন্দিকে। ঝারখণ্ডে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতি এখন হিন্দির মাধ্যমেই শিাপ্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করতে চাচ্ছে বিদ্যা। বাংলাদেশে ঝাড়খণ্ডের তুলনায় সাঁওতালদের সংখ্যা নগণ্য। অথচ আমাদের লে. জেনারেল মহোদয় বলছেন, সাঁওতালি ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে। বিএনপির একজন কথিত উপদেষ্টা বলে পরিচিত ব্যক্তি কেন, কী কারণে জাতিকে বাদ দিয়ে উপজাতি নিয়ে রাজনীতি করতে উৎসাহিত হচ্ছেন, সেটা আমার কাছে মোটেও স্বচ্ছ মনে হলো না।
বাংলাদেশে সাঁওতালদের পরে সবচেয়ে বড় উপজাতি হিসেবে ধরা হয় চাকমাদের। চাকমারা সবাই মঙ্গোলীয় মানবধারার মানুষ। তাদের দেখে এ দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি থেকে সহজেই পৃথক করে চিনতে পারা যায়। এ দেশে মঙ্গোলীয় মানবধারার মানুষের মধ্যে দু’টি উপধারা ল করা যায়। একটির মাথার আকৃতি হলো মাঝারি। আর অন্যটির মাথার আকৃতি গোল। মাঝারিদের বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে গারো এবং খাসিয়াদের কথা। অন্য দিকে, গোল মাথার মঙ্গোলীয়দের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো চাকমা ও মারমারা। মঙ্গোলীয় মানবধারার গণ্ডের হাড় হয় উঁচু। এ জন্য তাদের মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় সমতল। এ ছাড়া তাদের চোখের ওপরের পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ। যে কারণে তাদের চোখ দেখে মনে হয় ছোট এবং বাঁকা। মঙ্গোলীয় মানবধারার মানুষের পুরুষের মুখে গোঁফ-দাড়ি হয় না বললেই চলে। যদিও মারমা ও চাকমাদের চেহারার মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে এবং যদিও তারা উভয়ই অতীতে এসেছে আরাকান থেকে। তবু তাদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। মারমাদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। যা তারা লিখে বর্মি অরে। কিন্তু চাকমাদের এখন আর কোনো নিজস্ব ভাষা নেই। বাংলাই হয়ে উঠেছে তাদের মাতৃভাষা। চাকমারা হয়ে উঠেছে শতকরা ষাট ভাগ শিতি। তাদের আর বলা চলে না একটা উপজাতি। মনোভাবের দিক থেকে তারা হয়ে উঠেছে হিন্দুভাবাপন্ন। যদিও তারা নিজেদের দাবি করে বৌদ্ধ। কিন্তু তারা একই সাথে আবার লক্ষ্মীপূজাও করে। তাদের তুলনায় মারমারা অনেক খাঁটি বৌদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম একসময় ছিল একটি জনবিরল অঞ্চল। ১৯৪৭ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামকে র্যাডকিফ প্রদান করেন তদানীন্তন পাকিস্তানকে, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২ ভাগের কাছাকাছি।
চাকমা নেতা স্নেহ কুমার ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাঙ্গামাটিতে উত্তোলন করেন ভারতের অশোকচক্র সংবলিত ত্রিরংরঞ্জিত পতাকা। যেটাকে একুশে আগস্ট অস্ত্র হাতে বালুচ রেজিমেন্টের লোকদের গিয়ে টেনে নামাতে হয়েছিল। চাকমারা ভারতের পতাকা নামাতে চেয়েছিল না। মার্কিন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান মিশনারি রিচার্ড টিম কারিতাসের দ্বিমাসিক মুখপত্র বিনিময়-এর ১৩ বর্ষ: ফেব্রয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যায় লিখেছেন, র্যাডকিফ জিন্নাহ সাহেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে দিয়ে দেন সাবেক পাকিস্তানকে। যেটা ছিল একটা চরম অবিচার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনিতেই আসেনি সাবেক পাকিস্তানে। জিন্নাহ সাহেব এর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলাকে। তিনি এটা করেছিলেন তদানীন্তন পূর্ববাংলার একমাত্র সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে। এখন গুরুদাসপুরের মধ্যে যে ভারত অনেক সহজে কাশ্মিরে সৈন্য পাঠাতে পারছে। গুরুদাসপুর পেয়ে ভারত হয়েছে যথেষ্ট লাভবান।
ফাদার টিম চেয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে পৃথক হয়ে যাক। কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই ও বম উপজাতি ইতোমধ্যেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আরো অনেক উপজাতি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লাগোয়া মিজরাম রাজ্যে মিজুরা সবাই গ্রহণ করেছে খ্রিষ্টধর্ম। উপজাতি নিয়ে রাজনীতি করতে দেখা যাচ্ছে বামপন্থীদের। আর দেখা যাচ্ছে বিদেশী খ্রিষ্টান মিশনারিদের।
বাংলাদেশে এখন মোট উপজাতির সংখ্যা ঠিক কত, আমার তা জানা নাই। তবে যত দূর জানি উপজাতিদের একত্রিত জনসংখ্যার পরিমাণ হলো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের কাছাকাছি। সংখ্যাটা মোটেও বড় নয়। কিন্তু উপজাতিরা বাস করছে ভারত-বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে। সীমান্তের উভয় পাশে অনেক েেত্রই একই উপজাতির বাস। তাই উপজাতি নিয়ে রাজনীতি যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।
আওয়ামী লীগ সরকার চাকমাদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছে। মেনে নিয়েছে উপজাতিদের পৃথক সত্তার বাস্তবতাকে। যদিও শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্র“য়ারি রাঙ্গামাটি গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, দেশের সব লোক বাঙালি বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ যা করেছে সেটা শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। অবশ্য যে চুক্তি হয়েছে সেটা পার্লামেন্টের মাধ্যমে হয়নি। এটাকে তাই বৈধ চুক্তি বলা চলে না। চুক্তিতে স্বার করেছেন সপ্তম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য জনসংহতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। তাই এই চুক্তির কোনো আইনগত বৈধতা নেই। এ ছাড়া সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সব উপজাতির প্রতিনিধি নন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে এ েেত্র কোনো চুক্তি হতে পারে না।
আরাকানের (রাখাইন প্রে) ইতিহাস থেকে জানা যায়, আরাকানের এক রাজা মেং সোআ মংউন ১৪৩০ সালে ব্রহ্মের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন গৌড়ের সুলতান জালাল আল দ্বীন মুহাম্মদ শাহর কাছে। তিনি আরাকানের রাজাকে যথেষ্ট সৈন্য দেন তার রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। আরাকানের রাজা যুদ্ধে জিতে তার রাজ্য ফিরে পান। নতুন রাজধানী হয়, যার নাম রোহং।
আরাকানের রাজার সাথে গৌড় থেকে যে সেনাবাহিনী যায় ও থাকে রোহং-এ, তাদের বংশধরকে বলে রোহিঙ্গা। আরাকানের রোহং শহরের নাম থেকে উদ্ভব হয় রোসাঙ্গ নামের। বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে উল্লেখ করা হয়েছে রোসাঙ্গ হিসেবে। আরাকানের রাজারা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। তাদের ভাষা ছিল আরাকানে প্রচলিত প্রাচীন বর্মি ভাষা। কিন্তু যেহেতু তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল গৌড়ের সাথে, তাই তারা বাংলাভাষা শিখতেন ও জানতেন। আরাকানের রাজসভায় তাই সপ্তদশ শতাব্দীতে হতে পেরেছে বাংলা ভাষার বিশেষ চর্চা। উদ্ভব হতে পেরেছে দৌলত কাজী, আলাওলের মতো কবির সপ্তদশ শতাব্দীতে। এখন রোহিঙ্গাদের আরাকান থেকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়ানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চাকমা রাজনীতি নিতে পারে একটা ভিন্ন রূপ। সন্তু লারমাদের পে হাত মেলানো অসম্ভব নয় মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে। এই পরিপ্রেেিত আমাদের দেখা উচিত হবে বাংলাদেশের উপজাতি রাজনীতিকে।
দৈনিক নয়াদিগন্ত/ ২৬ নভেম্বর ২০১৬।