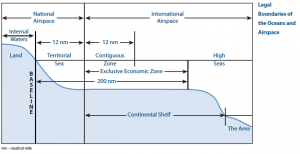ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ ডেভিড প্রেন ১৯০৩ সালে ‘বেঙ্গল প্ল্যান্টস’ নামে একটি বই লিখেন। তিনি যখন বইটি লিখেন, তখন বেঙ্গল বলতে বুঝিয়েছে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকেই। এর মধ্যে পড়ে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড। তিনি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাছপালার জরিপ করে বিবরণ দিয়েছেন তার বেঙ্গল প্লান্টস বইতে। তার এ বইটি পড়ে এখনো এই অঞ্চলের গাছপালা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রেনের মতে, সুন্দরবন নামটি এসেছে সুঁদরী (Heritiera minore, Roxb) গাছের নাম থেকে। কিন্তু সুঁদরী গাছ হয় কেবল সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে, যা পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে; কিন্তু সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, সে অংশে প্রধান গাছ হলো গরান। ওই অংশে সুঁদরী গাছ ছিল না; কিন্তু তবুও ওই অংশকে বলা হয়েছে সুন্দরবন। যদিও বলা উচিত ছিল, গরান (Ceriops roxburghiana, Aran) বন; কিন্তু তা বলা হয়নি।
অনেকে বলেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে সমুদ্র-বন থেকে। সমুদ্র-বন বলতে বুঝিয়েছে সমুদ্রের ধারের বন। আজ যেখানে সুন্দরবন; অনেকের মতে, একসময় সেখানে বন ছিল না। ছিল জনবসতি। সুন্দরবনের মাটি খুঁড়ে শান বাঁধানো পুকুরঘাট ও বাড়ির ধ্বংসাবশেষ অবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয়, ওই অঞ্চলে এক সময় জনবসতি ছিল। মেজর জেমস রেনল, যিনি প্রথম জরিপ করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র আঁকেন (১৭৬৪-৭৬ খ্রি:), তিনি বলেছেন, তিনি বয়স্ক লোকদের মুখে শুনেছেন, একসময় সুন্দরবন ছিল না। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারে ওই অঞ্চল থেকে মানুষ অন্যত্র চলে যায়। গড়ে ওঠে বনভূমি। সুন্দরবনের বয়স খুব বেশি নয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতের প্রতœতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে দু’টি সুন্দর কষ্টিপাথরের মূর্তি পেয়েছে। এই মূর্তি দু’টি কলকাতার বিখ্যাত ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অভিমত হলো, এখন পশ্চিমবঙ্গের যেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন, একসময় সেখানে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। ব্রিটিশ শাসনামলে সুন্দরবনে বাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি ঠেকানো হতো। তারপর বাঁধের এক পাশের সুন্দরবনে আগুন ধরিয়ে গাছপালা পোড়ানো হতো। পোড়ানো গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে বের করা হতো চাষের জমি। এই নোনা জমিতে প্রথমে চাষ করা যেত না। কয়েক বছর ব্যবস্থা করা হতো নোনা জমি থেকে বৃষ্টির পানিতে লবণ ধুয়ে যাওয়ার। তারপর নোনা জমি পরিণত হতো মিঠা জমিতে। এই মিঠা জমিতে আরম্ভ করা হতো চাষাবাদ।
সুন্দরবনের জমি খুবই উর্বর। বিনা সারে এখানে ধান লাগিয়ে প্রচুর ধান উৎপাদন করা হতো। সে আমলের ব্রিটিশ সরকারি কৃষি বিভাগ এভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষিভূমি গড়ার কাজে উৎসাহ দিতেন। লক্ষ্য ছিল এ দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এখন আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা তুলছেন সুন্দরবন রক্ষার আওয়াজ; কিন্তু ইংরেজ আমলে এই আওয়াজ ওঠেনি। ইংরেজ আমলে খাদ্য সমস্যা সমাধানের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, নরখাদক বাঘ, কুমির ও বিষধর সাপ রক্ষা করার ওপর নয়। ইংরজে আমলে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার বাঘ ও সাপকে মারার জন্য দিতেন পুরস্কার। কারণ এ দেশে বহু লোক মারা যেত সাপের কামড়ে এবং বন্যবাঘের আক্রমণে। বাঘের উপদ্রব এমনই ছিল যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করতেন। পূজা করতেন বাঘের পেটে না যাওয়ার জন্য; কিন্তু এখন বাংলাদেশে মানুষ গৌরব করছে, সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে। আন্দোলন করছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষা করার জন্য। আমাদের মনমানসিকতায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। এখন বোঝানো হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে হবে। তা তারা মানুষের যত শত্রুই হোক। রক্ষা করতে হবে পাখিদের, তা তারা ধানক্ষেতের ধান খেয়ে যত ক্ষতি সাধনই করুক না কেন। অর্থাৎ, মানুষের জীবনের চেয়ে অন্য প্রাণীর জীবনকে ভাবা হচ্ছে অনেক বেশি মূল্যবান।
অথচ জীববিজ্ঞানের বই পড়লে আমরা দেখি, বর্তমানে স্তন্যপায়ী জীবের প্রজাতি-সংখ্যা হচ্ছে তিন হাজার ৫০০। এ যাবৎ দুই হাজার ৫০০ স্তন্যপায়ী প্রজাতি-সংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে মানুষের কারণে নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। অন্য শ্রেণীর প্রাণীদের কথা আমি এখানে টেনে আনতে চাচ্ছি না। আমরা মানুষ। স্তন্যপায়ী প্রাণী। এসব স্তন্যপায়ী প্রাণী ও আমরা হলাম একই শ্রেণিভুক্ত। জীববিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন, বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এই বিলুপ্ত হওয়াই সব সত্য নয়। আবির্ভাব ঘটেছে অনেক নতুন প্রজাতির প্রাণীর। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, বর্তমান মানুষ একদিন বিলুপ্ত হতে পারে, আর তার স্থানে আবির্ভাব ঘটতে পারে মানুষের চাইতে উন্নত বুদ্ধিবান প্রাণীর। জীব বিবর্তনের ধারা থেমে যায়নি।
ফরহাদ মজহার বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী। কেউ কেউ মনে করেন, তাকে নাকি বলা চলে বাংলাদেশের কার্লমার্কস। তার সম্পর্কে আমি যথেষ্ট জানি না। তিনি আমার চেয়ে বুদ্ধিতে ছোট না হলেও বয়সে অনেক ছোট। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে হয়তো বা আমি হতে পারতাম তার শিক্ষক। অবশ্য তার বয়সের সত্যিকার হিসাব আমার জানা নেই। তিনি এমন কতগুলো কথা বলেছেন (নয়া দিগন্ত: ২০ আগস্ট ২০১৬), যা আমাকে খুব বিস্মিত করেছে। তাই এ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আমি কিছু মন্তব্য না করে পারছি না। তিনি বলেছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি মানুষের খুব ক্ষতি করছে। এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে; কিন্তু যেসব দেশকে আমরা ধরি অর্থনীতির দিক থেকে অগ্রসর, তাদের কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালাতে যে শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে, তার ৪০ শতাংশ আসছে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য থেকে; ৩৮ শতাংশ আসছে পাথুরে কয়লা ও লিগনাইট থেকে। বাদবাকি শক্তি আসছে প্রাকৃতিক গ্যাস, নদীপ্রবাহ, পারমাণবিক কেন্দ্রের বিক্রিয়া ও অন্যান্য উৎস থেকে। ফরহাদ মজহারের উপদেশ অনুসরণ করতে গেলে আমাদের দেশে কলকারখানার অর্থনীতির যে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। চলবে না রেলগাড়ি, বাস ও বিমান। তোলা যাবে না ডিপ টিউবওয়েলে সেচের পানি। চাষের কাজে ব্যবহার করা যাবে না পাওয়ার টিলার। আমার কাছে তাই তার বক্তব্যকে মনে হয়েছে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।
আমি ও আমার মতো অনেকেই ভারতের সাথে কেবল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নয়, কোনো যৌথ কোম্পানি স্থাপন করতে চাই না। এর কারণ, ভারতের সাথে আমাদের রয়েছে ঐতিহাসিক বিরোধ। বলতে গেলে জ্ঞাতিশত্রুতা। এমনি শত্রুতা যত সহজে মেটে, জ্ঞাতিশত্রুতা তত সহজে মেটে না। আমাদের অভিজ্ঞতা এ রকমই ভাবতে বলে। অনেক কিছুই ঘটছে সমকালে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে যেমন করতে চাচ্ছে রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, তেমনি আবার শেখ হাসিনা চীনের সাথে চুক্তি করছেন বাংলাদেশের রণতরী নির্মাণের; ভারতের সাথে নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে খুবই জটিল। যাকে ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আমরা রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্র চাচ্ছি না; কিন্তু আমাদের যুক্তি হলো রাজনৈতিক। এর জন্য আমরা দিতে চাচ্ছি না সুন্দরবনের ধ্বংস হওয়ার অজুহাত। সুন্দরবন ধ্বংস হবে না। চর পড়ে বাংলাদেশের ভূমি বাড়ছে। আর সুন্দরবন ক্রমেই সরে যেতে চাচ্ছে আরো দক্ষিণে। অর্থাৎ নতুন সুন্দরবন যাচ্ছে গড়ে উঠতে। আমাদের তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। আমাদের দেশের পরিবেশবাদীরা বুঝতে অক্ষম যে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির দান নয়; তা হলো মানুষেরই চেষ্টার ফল। মানুষকেই চেষ্টা করতে হবে পরিবেশকে সুন্দর রাখার এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ার।
ফরহাদ মজহারের লেখাটি পড়ে জানলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্ররা সম্প্রতি বিক্ষোভ করেছেন ভারতীয় হাইকমিশনারের বিপক্ষে। বিষয়টি আমার কাছে ভালো লাগল। কেননা সবাই জানেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হয়ে উঠেছে ভারতীয় চক্রান্তের অন্যতম ঘাঁটি। চারুকলা বিভাগ থেকে বাঙালি সংস্কৃতির নামে করা হচ্ছে হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা। জ্বালানো হচ্ছে বাংলা নববর্ষে মঙ্গলপ্রদীপ। আমি মনে করি, এই চক্রান্তের দিন ফুরিয়ে আসারই পথে। বাংলাভাষী মুসলমানের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা হলো বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি। একটু ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। হয়তো তা বর্তমান আলোচনায় একেবারে অপ্রাসঙ্গিকও হবে না। যদিও বা সুন্দরবন রক্ষার আওয়াজের সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। গ্রামবাংলার মুসলিম মহিলারা খুব সুন্দর কাঁথা সেলাই করেন। এটা বাংলাদেশের শিল্পকলার হলো একটি সনাতন নিদর্শন। বাঙালি মুসলিম মহিলারা কাঁথায় নকশা করেন ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক আকার-আকৃতির সাহায্যে। তারা প্রাণী ও মানুষের নকশা-মুদ্রা (Motif) যথেষ্ট ব্যবহার করেন না। তারা অনুসরণ করে চলেছেন, মুসলিম নকশাকলা বা অ্যারাবেস্কের (Arabesque) ঐতিহ্য, যাকে বলা হয় মুসলিম শিল্পকলা, তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদ্ভিদীয় ও জ্যামিতিক অলঙ্করণের প্রাণশক্তি। মুসলমান সমাজে কাঁথাকে বলা হয় ‘খ্যাঁতা’। খ্যাঁতা শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আরবি ‘খাইতান’ শব্দ থেকে। আরবিতে খাইতান মানে হলো সেলাই করা। এ দেশে মানুষ সেলাই করা জামা পরত না। সেলাই করা জামা পরা আরম্ভ হয় তুর্কি মুসলিম নৃপতিদের শাসনামল থেকে। যারা কাপড় কেটে সেলাই করে জামা বানান, তাদের বাংলায় বলা হয় ‘খলিফা’। এই খলিফা শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আরবি খাইতান শব্দ থেকে। দর্জি শব্দটি আরবি নয়। ফারসি ভাষার; কিন্তু বাংলায় দর্জি ও খলিফা শব্দ দু’টি একই অর্থবোধক। এর কোনো সংস্কৃত প্রতিশব্দ নেই।
অনেকে মনে করেন, বাংলা কাঁথা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘কন্থা’ শব্দ থেকে; কিন্তু মনে করার কারণ আছে, কাঁথা সেলাই আগে এ দেশে ছিল না। দেখে খুশি হলাম, ঢাকার চারুকলা অনুষদের ছাত্ররা হয়ে উঠেছেন যথেষ্ট আত্মসচেতন। তাদের উচিত হবে, দেশের ইসলামি শিল্পকলার ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাদের আন্দোলন কেবলই থেমে থাকবে না রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে। ইসলামি শিল্পকলা কোনো ধর্মনির্ভর শিল্পকলা নয়। এর লক্ষ্য থেকেছে চারুতার সৃষ্টি।
আমি নয়া দিগন্তে লিখি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। আমার মতামত একান্তভাবেই আমার নিজের। এর সাথে নয়া দিগন্তের মতামতের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। বর্তমান প্রবন্ধে যা বললাম, সেটাও আমার নিজস্ব মতামত। এর মধ্যে নয়া দিগন্তের কোনো সম্পৃক্ততা খোঁজা উচিত হবে না। ফরহাদ মজহার হলেন নয়া দিগন্তের একজন বাছাই করা লেখক। তার লেখা নয়া দিগন্তে যতটা জায়গা পায়, খুব কম লেখকের লেখাই তা পেয়ে থাকে। বর্তমান লেখায় আমি ফরহাদ মজহারের লেখা সম্পর্কে যা বললাম, সেটা আমার নিজস্ব মতামত। নয়া দিগন্তের একজন পাঠক হিসেবে এ রকম মতামত ব্যক্ত করা গণতান্ত্রিক নীতিবিরুদ্ধ হলো না বলেই আমি মনে করি।
দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ আগস্ট ২০১৬।